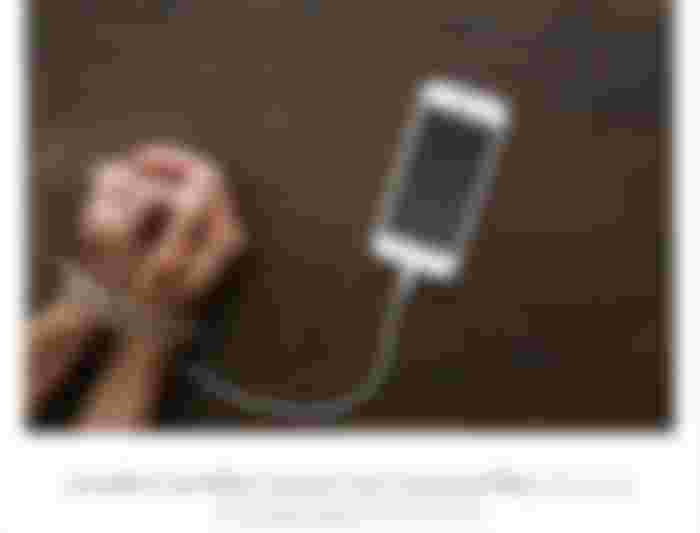লজ্জা ও সামাজিক (সোশ্যাল)ফোবিয়া
সোশ্যালফোবিয়া কাকে বলে?
লজ্জা একধরনের অস্বস্তি যা আমাদের অনেকের হয়ে থাকে।অল্পস্বল্প হলে এতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমাদের অনেকের অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জা করে, কিন্তু প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে গেলে আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি, এমনকি উপভোগও করতে পারি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা।
আপনার সোশ্যাল ফোবিয়া থাকলে আপনি অচেনা লোকের সামনে খুব অস্বস্তিবোধ করবেন। আপনার মনে হবেঃ
1.সবাই আপনাকে অপছন্দ করছে
2.আপনি এখনি কী করতে কী করে বসবেন
এই অনুভূতি এতই কষ্টকর হতে পারে যে আপনি হয়ত লোকের সঙ্গে মেলামেশাই করতে পারবেন না। সব সামাজিক অনুষ্ঠান আপনি এড়িয়ে যাবেন।
প্রধানতঃ দুধরনের সোশ্যাল ফোবিয়া দেখা যায়ঃ
সাধারণ (বা জেনেরালাইজেড) এবং স্পেসিফিক
জেনেরাল সোশ্যাল ফোবিয়াঃ
এতে আপনিঃ
1.মনে করেন যে লোকে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখছে
2.মনে করেন যে তাঁরা আপনি কী করছেন না করছেন তার উপর নজর রাখছে
3.অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন না
4.দোকানে বা রেস্তোরাঁতে যেতে চাইছেন না
5.লোকের সামনে খেতে অসুবিধা হচ্ছে
6.স্বল্প পোশাকে বাইরে বেরোতে চাইছেন না (যথা সমুদ্রের ধারে)
7.প্রয়োজন সত্ত্বেও স্পষ্ট করে নিজের মনোভাব জানাতে দ্বিধাবোধ করছেন
পার্টিতে যাওয়া বিশেষ করে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। মনে মনে চাইলেও আমরা অনেকেই ঘরভর্তি লোকের সামনে যেতে দ্বিধাবোধ করি। সোশ্যাল ফোবিয়া থাকলে আপনি ঘরেও দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, ভিতরে ঢুকতে কুন্ঠাবোধ করবেন। এতে সকলে ভাবতে পারে যে আপনার ক্লস্ট্রোফোবিয়া(বদ্ধ ঘরে ফোবিয়া)আছে। শেষমেষ আপনি যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন আপনার মনে হবে যে সবাই আপনাকে দেখছে। অনেকে পাব বা পার্টিতে যেতে গেলে তার আগে মদ্যপান করে নেন যাতে একটু রিল্যাক্সড বোধ করেন এবং পার্টিটা উপভোগ করেন।
স্পেসিফিক সোশ্যাল ফোবিয়াঃ
এটি দেখা যায় কিছু লোকের মধ্যে যাঁদের কাজের ধরনই এমন যে তাঁদের মধ্যমণি হতে হয়। নায়ক, গায়ক, শিক্ষক বা ইউনিয়নের নেতা প্রমুখরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। স্পেসিফিক সোশ্যাল ফোবিয়া থাকলে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু সবার সামনে যখন দাঁড়িয়ে কথা বলতে বা গান গাইতে গেলে টেনসন হয় এবং কেউ কেউ তোতলাতে থাকেন। এমনকী যাঁরা অভিজ্ঞ, এবং এই কাজ প্রায়ই করে থাকেন তাঁদের হঠাৎ এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এমনও হতে পারে যে লোকের সামনে একটাও কথা বলা যায় না, একটা প্রশ্ন অবধি করা যায় না।
কী রকম অনুভূতি হয়?
দুধরনের ফোবিয়াতেই স্ট্রেসের উপসর্গ দেখা দেয়। আপনি দেখবেন যে আপনিঃ
1.খুব চিন্তা করছেন যে লোকের সামনে অস্বাভাবিক কোনো আচরণ না করে ফেলি
2.যেখানে যেতে আপনার মন চাইছে না, সে বিষয়ে সবসময় ভেবে যাচ্ছেন
3.মনে মনে ভাবছেন কবে কখন কোন পরিস্থিতিতে আপনি লজ্জায় পড়েছিলেন
4.আপনি যা করতে চান বা বলতে চান তা পারছেন না
একটা ঘটনার পর বার বার ভাবছেন ‘কী করলাম, কী করলাম’
5.আপনি হয়ত বার বার পুংখানুপুংক্ষ ভাবে নিজের মনে ভাববেন কী করা উচিৎ ছিল বা বলা উচিৎ ছিল।
এই দুধরনের সোশ্যাল ফোবিয়াতেই কিছু শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন ধরুনঃ
1.মুখ শুকিয়ে যাওয়া
2.অতিরিক্ত ঘামা
3.বুক ধড়ফড় করা
4.বারবার পেচ্ছাপ বা পায়খানা পাওয়া
5.হাত বা পা ঝিমঝিম করা বা অসাড় হয়ে যাওয়া (এটি হয় কারণ আপনি খুব দ্রুত নিশ্বাস নিচ্ছেন)
অন্যেরা হয়ত আপনাকে দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনি অস্বস্তিতে পড়েছেন। আপনি হয়ত লাল হয়ে যাচ্ছেন, তোতলাচ্ছেন বা আপনার হাত পা কাঁপছে। এই উপসর্গগুলি আপনার ভীষণ ভয়ানক মনে হতে পারে এবং আপনার টেনসন আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।
এরপর এটি বাড়তে থাকে চক্রাকারে। আপনি টেনসন নিয়ে টেনসন করেন এবং তাতেই আরো বেড়ে চলে আপনার টেনসন। আপনার চোখেমুখে ফুটে ওঠে এর অভিব্যাক্তি। আপনার টেনসনই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু।
প্যানিক
দুধরনের সোশ্যাল ফোবিয়াতেই প্যানিক হতে পারে। প্যানিক বেশিক্ষণ থাকে না, মিনিট কয়েক মাত্র থাকে। সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা হয়, মনে হয় আপনি পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন। আপনার মনে হয় আপনি এবার হয় মারা যাবেন নয়ত পাগল হয়ে যাবেন। সচরাচর যে পরিস্থিতিতে এটি হয়েছে সেখান থেকে আপনি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। প্যানিকের অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, এটি কেটে গেলে আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন। প্যানিক যতই ভয়প্রদ হোক না কেন, এতে আপনার শারীরিক কোনো ক্ষতি হবে না এবং নিজের থেকেই এটি কমে যাবে।
কিভাবে এতে জীবন প্রভাবিত হয়?
অনেকে নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে এই সমস্যার মোকাবিলা করেন। এর অর্থ তাঁরা এবং তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যেরা যা করতে ভালবাসতেন তা অনেক সময় না করা। তাঁরা বাচ্ছার স্কুলে যেতে পারেন না, ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পারেন না বা বাজার করতে যেতে পারেন না। এমনকী তাঁরা অনেক সময় নিজেদের পদোন্নতিতেও বাধা দেন যদিও তাঁদের পক্ষে চাকরির উন্নতির পথে আর কোনো বাধা নেই। যাঁদের সোশ্যাল ফোবিয়া থাকে তাঁদের অর্ধেকের বেশি (বিশেষত; পুরুষরা) দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন না।
এতে কজন আক্রান্ত হয়?
একশো জনের মধ্যে পাঁচ জনের সোশ্যাল ফোবিয়া থাকে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি দুতিনগুণ বেশি দেখা যায়।
এর থেকে আর কী হতে পারে?
বিষাদরোগ
সোশ্যাল ফোবিয়া থেকে বিষন্নতার জন্ম হতে পারে। শেই বিষাদরোগ এত বেশি তীব্র হতে পারে যে তার জন্য আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।
আগারোফোবিয়া
আপনি যদি সবসময় যেখানে মানুষ আছে সেই জায়গায় না যান তবে এই জায়গাগুলির প্রতি আপনার ভীতি জন্মাতে পারে। এমনকী আপনি নিজের বাড়ী ছেড়ে বেরোতেও ভয় পেতে পারেন—তাকে বলে আগারোফোবিয়া।
মদ ও অন্য নেশা
আপনি হয়ত আপনার মনের কষ্ট লাঘব করতে মদ, ড্রাগ বা ঘুমের ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন। এর ফলে আপনি মাদকাসক্ত হয়ে যেতে পারেন।
শারীরিক স্বাস্থ্য
প্যানিক এবং চিন্তা সত্ত্বেও হার্টের অসুখের সম্ভাবনা কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সমান, বেশি না।
কেন সোশ্যাল ফোবিয়া হয় ?
আমরা সঠিক জানিনা। এতে বেশি আক্রান্ত হয় তাঁরা যাঁরা
1.লোকসমক্ষে নিজেদের ব্যবহার সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন
2.অল্পবয়সে তোতলামিতে ভুগতেন
তিন থেকে সাত বছর বয়সে এই ধরনের লজ্জা স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে জাগে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে জীবনের এই অধ্যায় থেকে এগোতে না পারলে সোশ্যাল ফোবিয়া জন্ম নেয়।
এই অসুবিধা না কাটবার কারণ কী ?
চিন্তা
সামাজিক পরিস্থিতিতে কিছু চিন্তা মনে আসে। যেমন ধরুনঃ
1.‘আমায় সবসময়ে সবাই বুদ্ধিমান ভাববে পরিস্থিতি যেন আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে’
2.‘আমি খুব বোরিং’
3.ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা—কেউ আমায় চিনলে সে বুঝতে পারবে আমি কেমন অপদার্থ
আপনি সব সময় নিজের ব্যবহার পুংখানুপুঙ্খভাবে বিচার করছেন এবং নিজের অক্ষমতা বা দোষগুণগুলো দেখছেন।
এই চিন্তা এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে আপনি এগুলি সত্য মনে করেন, যদিও এর সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আপনার নিশ্চিত ধারনা হয় যে সবার চোখে আপনাকে খারাপ লাগছে। অন্যলোকেরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনার সম্পর্কে অন্যরকম ধারনা মনে পোষণ করেন।
সাবধানতা অবলম্বন
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আপনি কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। যথাঃ
1.মদ্যপান
2.কারো চোখে চোখ না মেলানো
3.নিজের সম্পর্কে কোনো কথা না বলা
4.অন্যকে বেশি প্রশ্ন করা
এর ফলে আপনি কোনোদিন জানতেই পারেন না যে এই সাবধানতা অবলম্বন না করলেও আপনার কল্পিত ভয়ানক পরিণতি হয় না।
ঘটনার আগে এবং পরে যে চিন্তা হয়
একই ঘটনার আগে এবং পরে বারংবার চিন্তা করলে আপনার আরো বেশি নিজের দোষ চোখে পড়ে। আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়।
সাহায্যের পথ
কারো সোশ্যাল ফোবিয়া হলে নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী নীচের টিপসগুলি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।
আপনি নিজে কী করতে পারেন
1.আপনি স্বভাবতই লাজুক হলে লোকাল কোনো আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কোর্স করতে পারেন।
2.রিল্যাক্স করতে শিখুন। বই, টেপ, সিডি, ডিভিডি সব পাওয়া যায় রিল্যাক্সসেসান পদ্ধতি শেখানোর। আপনি দুশিন্তা শুরু হলেই রিল্যাক্স করলে বাড়াবাড়ি আটকে দিতে পারবেন।
3.আপনার দুশ্চিন্তাগুলি লিখে রাখুন। আপনার সম্পর্কে যে ছবি ফুটে উঠছে, লিখে রাখলে তার পরিবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।
4.আপনি নিজে মনে মনে কী ভাবছেন সেকথা চিন্তা না করে লোকে কী বলছে তা শোনার চেষ্টা করুন।
5.যে সাবধানতা আপনি অবলম্বন করেন, সেটা বন্ধ করুন। যেটি সহজতম সেটি দিয়েই শুরু করুন।
6.কোনো ভয়জনক পরিস্থিতি হলে তাকে ছোটো ছোটো ধাপে ভেঙ্গে দেখুন। প্রথম ধাপটি অভ্যাস করুন। অভ্যস্ত হতে সময় লাগতে পারে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরের ধাপে এগোন। তারপর তার পরের ধাপে। এমনি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলুন।
ভিনাস্ট্রাফোবিয়ার উৎপত্তি ও সংজ্ঞা
ভিনাস্ট্রাফোবিয়া মানে হলো সুন্দরী মেয়েদের ভয় পাওয়া। এই ফোবিয়ার নামকরণ করা হয়েছে রোমান দেবী ভেনাস থেকে। ভেনাসকে প্রেমের দেবী বলা হয়। এছাড়াও তাকে যৌনতা ও সৌন্দর্যের দেবী হিসেবেও দাবি করা হয়। ফোবিয়ার তিনটি প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ভিনাস্ট্রাফোবিয়া এগুলোর মধ্যে স্পেসিফিক ফোবিয়ার কাতারে পড়ে। একে ক্যালিগাইনিফোবিয়াও বলা হয়ে থাকে।
রোমান প্রেমের দেবী ভিনাসের নাম থেকে এসেছে ভিনাস্ট্রাফোবিয়া;
মানুষ স্বভাবগত দিক থেকেই সুন্দরের পূজারী। আর সুন্দরী মেয়েদের প্রতি সকলের এক আলাদা আকর্ষণ কাজ করে। তবে ভিনাস্ট্রাফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। এরা আকর্ষণীয় নারীদের আশেপাশে থাকতে একধরনের ভয় ও অস্বস্তি বোধ করে। এই অমূলক ভয়ের কারণে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীদের সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।
ভিনাস্ট্রাফোবিয়াকে গাইনোফোবিয়ার অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। গাইনোফোবিয়া বলতে সকল মেয়েদের ভয় পাওয়াকে বোঝায়। তবে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই দুই ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়। এরকম ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষ অনেক হীনম্মন্যতায় ভোগে। সুন্দরী মেয়েদের সামনে দাঁড়ালে তারা নিজেদের শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। তারা সত্যিকার অর্থেই অসুস্থ বোধ করে। নিজেদের অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় তাদের চোখে-মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়া, অনবরত ঘামতে থাকা ইত্যাদি তাদের মাঝে দেখা দেয়।
কারণ
কারো মাঝে একটি ফোবিয়া সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করে। পূর্বে ঘটে যাওয়া কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা এই অমূলক ভয়কে ট্রিগার করতে পারে। আবার এর পেছনে জেনেটিক বা বংশগত কারণও দায়ী। পূর্বপুরুষদের কারো কোনো মানসিক রোগ বা অন্য কোনো ফোবিয়া থাকলে তা থেকে এই রোগের উৎপত্তি ঘটতে পারে। তবে বেশিরভাগ স্পেসিফিক ফোবিয়ার কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করে আবির্ভাব ঘটে।
একজন ব্যক্তির অতীত জীবনে সুন্দরী মেয়েদের সাথে কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা, যেমন– হৃদয়ভঙ্গ হওয়া, জনসম্মুখে কোনো আকর্ষণীয় মেয়ের দ্বারা অপমানিত হওয়া ইত্যাদি মনে স্থায়ী আঘাত হানতে পারে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এক্ষেত্রে অনেক প্রভাব ফেলতে পারে। একজন ব্যক্তি কেমন পরিবেশে বড় হয়েছে তার সাথে এই ফোবিয়ার যোগসূত্র তৈরি করা যায়।
আগে থেকে থাকা কোনো মানসিক রোগ, যেমন- অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, জেনারালাইজড এংজাইটি ডিজঅর্ডার কিংবা অন্য কোনো এংজাইটি ডিজঅর্ডার থেকে এই ফোবিয়া আসতে পারে। এরকম কিছু মানসিক ডিজঅর্ডার ও অতীত খারাপ অভিজ্ঞতা একসাথে হানা দিলে এই অদ্ভুত ফোবিয়ার শিকার হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।
একজন ভিনাস্ট্রাফোবিককে যেভাবে চিনবেন
যে ব্যক্তির ভিনাস্ট্রাফোবিয়া রয়েছে তাকে ভিনাস্ট্রাফোবিক বলে। সাধারণ মানুষজনের সাথে তাদের আচরণ ও সুন্দরী মেয়েদের সামনে তাদের আচরণের মাঝে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর পেছনে কী কী কারণ কাজ করে তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলোর দরুণ একজন ভিনাস্ট্রাফোবিকের মস্তিষ্কে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটতে থাকে। এগুলো তার ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
যে লক্ষণগুলো সচরাচর একজন ভিনাস্ট্রোফোবিকের মাঝে দেখা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হলো:
১) মেয়েদের সামনে প্রচন্ড অস্বস্তি বোধ করা।
২) সুন্দরী মেয়েদের চিন্তা মাথায় আসলে ইতঃস্তত বোধ করা।
৩) তাদের সাথে বাধ্য হয়ে কথা বলতে হলে ঘামতে থাকা, চোখে-মুখে এক ধরনের অনীহা ফুটে ওঠা।
৪) আকর্ষণীয় মেয়েরা থাকতে পারে এমন জায়গা পরিত্যাগ করা।
৫) অকারণে হীনম্মন্যতা ও লজ্জা অনুভব করা।
৬) নিজেকে একঘরে করে রাখা।
মূলত আগে থেকে ওসিডি বা জিএডি নামক মানসিক রোগ থাকা মানুষের মাঝে এই ফোবিয়া থাকার সম্ভাবনা বেশি। আসলে ফোবিয়া নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। তবে এই ফোবিয়া কারো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্ত করলে অবশ্যই ভালো কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতে হবে।
ভিনাস্ট্রাফোবিয়ার চিকিৎসা
সাধারণত ফোবিয়াগুলোর সরাসরি কোনো চিকিৎসা নেই। তবে এগুলো মানসিক রোগের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় কিছু মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে বিভিন্ন থেরাপি নেওয়া যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টক থেরাপি ও এক্সপোজার থেরাপি। টক থেরাপির মধ্যে একটি হলো কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপি (সিবিটি)। এই থেরাপির মাধ্যমে রোগী কোনো থেরাপিস্টের সাথে নিয়ম মেনে কথাবার্তা বলেন। নানা বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে তিনি নিজের ব্যবহার ও চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনতে চেষ্ঠা করেন।
এক্সপোজার থেরাপি বলতে সরাসরি নিজের ভয়ের মুখোমুখি হওয়াকে বোঝায়। সুন্দরী মেয়েরা সচরাচর যেসব জায়গায় যায় সেখানে গিয়ে স্বেচ্ছায় নিজের ভয়ের মোকাবিলা করতে হয়। এভাবে চেষ্টা করতে থাকলে আস্তে আস্তে এই ফোবিয়া কেটে যেতে পারে।
সাইকোথেরাপি এই ফোবিয়া থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে;
এন্টি–ডিপ্রেসেন্ট বা অন্য কোনো ধরনের ওষুধও ফোবিয়ার চিকিৎসা হতে পারে। তবে এসব ওষুধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
পৃথিবীতে বহু বিচিত্র ও অদ্ভুত ফোবিয়া রয়েছে। এই যেমন ধরুন, হাইড্রোফোবিয়া। এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষ আক্ষরিক অর্থেই পানিকে ভয় পায়। তারা পানি সহ্য করতে পারে না। প্যাপিরোফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষ কাগজ ভয় পায়। স্কোলিওনোফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষ স্কুলে যেতে ভয় পায়।
এরকম অদ্ভুত ফোবিয়াগুলোর তালিকা বলে শেষ করা যাবে না। ভিনাস্ট্রাফোবিয়া এসব অদ্ভুত ফোবিয়ার কাতারেই পড়ে। তবে সব রোগের মতো এই রোগগুলোরও চিকিৎসা রয়েছে। তাই চিকিৎসার ব্যাপারে অনীহা না দেখিয়ে দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।
কুকুরের ফোবিয়া:যে সব কারণে ভয় পায় কুকুর
১) অ্যাস্ট্রাফোবিয়া
বজ্রপাতে ভয় পায় কুকুর।
অ্যাস্ট্রাফোবিয়া হচ্ছে বজ্রপাতের শব্দে ভয় পাওয়া। কুকুরের সবচেয়ে সাধারণ ফোবিয়া এটি। অধিকাংশ কুকুরই অ্যাস্ট্রাফোবিয়াতে অল্পবিস্তর ভুগে থাকে। তবে ভয় পাবার মাত্রা কুকুরভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত বজ্রপাতের পূর্বেই কুকুর বুঝতে পারে কিছু একটা হতে চলেছে এবং যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করে। বজ্রপাতের সময় দেখা যায় অনেক কুকুরের কানগুলো অনেকটা চ্যাপ্টানো আর লেজ একেবারে গুটি পাকিয়ে থাকে। এরকম দেখলে বুঝতে হবে কুকুরটির অ্যাস্ট্রাফোবিয়ার খুবই হালকা পর্যায়ে আছে। কিন্তু অনেক কুকুরই বজ্রপাতের সময় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, যাকে সামনে পায় তাকে কামড় দেয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে কুকুরটির অ্যাস্ট্রাফোবিয়া গুরুতর পর্যায়ের। কখনোবা ভয়ের মাত্রা বেশি হলে কুকুরের পাকস্থলীতে গণ্ডগোল বাঁধে এবং বমি হয়। এই ফোবিয়া কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় গান। বজ্রপাত শুরুর পূর্বে কিংবা শুরু হলে কুকুরকে গান শোনালে অ্যাস্ট্রাফোবিয়ার ভয় অনেকটাই প্রশমিত হয়ে আসে।
২) আতশবাজি ফোবিয়া
উচ্চশব্দের আতশবাজি ভয় পাইয়ে দেয় কুকুরকে
বজ্রপাতের মতো আতশবাজি ভয় পাওয়াটাও কুকুরের একটি স্বাভাবিক ফোবিয়া। তবে ভয়ের মাত্রাটা বেশি হলেই সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, উজ্জ্বল আলো দেখে নয়, বরং আতশবাজির প্রচণ্ড শব্দই কুকুরকে বেশি বিব্রত করে। তবে অনেক কুকুরই ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আবার অনেকে নিজের কুকুরকে অভ্যাস করিয়ে নেন। সেক্ষেত্রে প্রথমে কম আওয়াজের ছোট আতশবাজি দেখিয়ে শুরু করা যেতে পারে। তবে যেসব কুকুরের ক্ষেত্রে সমস্যাটা প্রকট সেগুলোর জন্য ‘অ্যান্টি অ্যাংজাইটি’ ওষুধ বা সিডেটিভ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।
৩) সেপারেশন ফোবিয়া
প্রভুর বাড়ি ত্যাগের সময় একাকীত্বে ভোগে কুকুর;
উন্নত দেশের পোষা কুকুরের মধ্যে এই ফোবিয়া বেশি দেখা যায়। সেপারেশন ফোবিয়া বলতে কুকুরের একাকীত্বে ভোগার ভয়কে বোঝায়। সহজ ভাষায়, একটি কুকুর যখন মনে করে যে তার প্রভু তাকে পরিত্যাগ করবে, তখন সে এরূপ ফোবিয়ায় ভোগে। অফিসগামী মানুষের পোষা কুকুরগুলো এরূপ পরিত্যাজ্য হবার ফোবিয়ায় ভোগে। সাধারণত কুকুর যখন এর মালিককে বাড়ি থেকে বের হতে দেখে, তখন একে সেপারেশন ফোবিয়া পেয়ে বসে। আর তখন শত বারণ সত্ত্বেও সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং মালিকের পিছু নিতে চায়। এরূপ ফোবিয়ায় ভুগতে থাকা কুকুরকে বাড়িতে একা রেখে গেলে দিনকে দিন এর ফোবিয়া প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। এরা একাকী বাড়িতে সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে। সেপারেশন ফোবিয়া থেকে খুব সহজেই কুকুরকে মুক্ত করা যেতে পারে। বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং বাড়িতে ফেরার সময় যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে, যেন কুকুরটির কাছে কোনোভাবেই এমন মনে না হয় যে তার মালিক অনেক সময়ের জন্য চলে যাচ্ছে তাকে ছেড়ে।
৪) হাসপাতালের ভয়
প্রথমবার টিকাদানের সময় ভয় পায় কুকুর;
কুকুরকে সুস্থ রাখতে নিয়ম মাফিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান অনেকেই। আর এখানেও জন্ম হয় আরেক প্রকার ফোবিয়ার। এই ফোবিয়ায় ভোগা কুকুর বাড়ি থেকে বেরুতেই চাইবে না। আপনার উদ্দেশ্য বেড়াতে যাওয়া হলেও সে ভাববে আপনি তাকে কোনো পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই! এই ফোবিয়া সহজেই এড়ানো যেতে পারে খানিকটা সাবধানতা অবলম্বন করে। যখন কোনো কুকুরকে প্রথমবারের মতো পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এমনিতে হাসপাতালের অপরিচিত গন্ধ এবং নতুন যন্ত্রপাতি দেখে সে ভীত হয়ে পড়ে। সবশেষ ইনজেকশন দেয়ার সময় ভয়ের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চাইলেই সে ভীতিকর সেই স্মৃতি স্মরণ করে। তাই মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ এই যে, কুকুরটিকে প্রথমে কয়েকবার এমনিতেই পশু হাসপাতালে ঘুরিয়ে আনতে হবে যেন সেটি সেই পরিবেশকে সহজ করে নিতে পারে। পরে একদিন ইনজেকশন প্রয়োগ করলেও আর সমস্যা নেই।
৫) গাড়িতে চড়ার ভীতি
ধীরে ধীরে অভ্যাস করালে গাড়ি চড়ার ভয় কেটে যায় কুকুরের;
এক মাসের জন্য চলে যাচ্ছেন কোথাও বেড়াতে। এমন অবস্থায় আপনার প্রিয় পোষা কুকুরটিকে সাথে নিয়ে যাবেন সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোনো কারণে কুকুরটি আপনার সাথে গাড়িতে উঠতে আপত্তি জানায় তখন? শুধু আপত্তি নয়, আপনি জোর করে গাড়িতে তুললে সে আপনাকে কামড়ও বসিয়ে দিতে পারে! এর কারণ গাড়িতে চড়ার ফোবিয়া। আর সে ফোবিয়া সৃষ্টির পেছনে কোনো না কোনোভাবে আপনিই দায়ী। কীভাবে? কুকুরের প্রথম গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা যদি ভালো না হয়, সেটি এর মনে দাগ কেটে যায় এবং ফোবিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, কুকুরের প্রথম গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা যদি হয় কোনো দুর্গম উঁচু নিচু রাস্তায় ভ্রমণ, ছোটোখাট দুর্ঘটনা কিংবা পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, তাহলে সে আর দ্বিতীয়বার গাড়িতে উঠতে চাইবে না। এক্ষেত্রে কুকুরের গাড়ি চড়ার ভীতি সহজেই দূর করা যায় কয়েকটি আনন্দভ্রমণের মাধ্যমে।
৬) স্টেয়ার ফোবিয়া
সিঁড়ি দিয়ে নামতে ভয় পায় কুকুর;
স্টেয়ার ফোবিয়া বা সিঁড়িতে ওঠানামা করার ভয় সাধারণত যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে হয়ে থাকে। কুকুর শিশু অবস্থায় সিঁড়িতে চলাফেরার সাথে পরিচিত না হলে বড় হয়ে সে ফোবিয়াতে ভোগে। একটি কুকুর হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির কাছে গিয়ে থেমে গেলে এবং ইতস্তত করতে থাকলে ধরে নিতে হবে সে সিঁড়িতে উঠতে বা নামতে ভয় পাচ্ছে। এক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে জোর করে একে সিঁড়িতে উঠিয়ে দিলে অনেক সময় ভয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে ব্যথা পায়। আমেরিকায় পশু হাসপাতালে পায়ের ব্যথায় ভর্তি হওয়া অধিকাংশ কুকুরই সিঁড়ি থেকে পড়ে জখম হয়। প্রথমেই বড় সিঁড়িতে না নিয়ে ছোট ছোট সিঁড়িতে ওঠানামার অভ্যাস করিয়ে এই ভয় কাটানো যেতে পারে।
৭) মেনজ ফোবিয়া
পুরুষদের ভয় পায় কুকুর;
একটি কুকুর যখন সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তখন সে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী থাকে। তাই মেনজ ফোবিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অনেক পুরুষই প্রতি বছর ভীত কুকুরকে আদর করতে গিয়ে কামড় খান! হ্যাঁ, কুকুর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি ভয় পায়। তবে কিছু কুকুর পরিস্থিতির শিকার হয়ে যেকোনো পুরুষকেই বিপদ মনে করে। আর এরূপ ফোবিয়া যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। কুকুরকে নানাভাবে বিরক্ত না করে বন্ধুসুলভ আচরণ করলেই এই ফোবিয়া ধীরে ধীরে কেটে যায়।
৮) অপরিচিতি ভীতি
অপরিচিত মানুষের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ফোবিয়ায় ভোগা কুকুর;
অপরিচিত মানুষ দেখলে কুকুর খানিকটা গর্জে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কুকুরের এই আচরণ বরং বাড়িঘরে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে। কিন্তু আচরণ যখন উল্টো হবে, তখন বুঝতে হবে সেটি ফোবিয়াতে ভুগছে। অপরিচিত মানুষকে ভয় পাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায় অনেক কুকুরের মাঝেই। আর কুকুরের এ সমস্যাটি একটি জটিল সমস্যা। কারণ, বাড়িতে আগত প্রতিটি নতুন মানুষের সাথে একে পরিচয় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি কুকুর যেখানে অপরিচিত লোকজন দেখে ঘেউ ঘেউ করলেও সহজে আক্রমণ করে না, বরং প্রভুর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কিন্তু ফোবিয়াতে ভোগা একটি কুকুর অপরিচিত মানুষ দেখলেই বিপদের গন্ধ পায় এবং ভয় পেয়ে আক্রমণ করে বসে। এরূপ ফোবিয়ায় ভোগা কুকুরকে কিছুদিন বেঁধে রাখলে এর ফোবিয়া কেটে যায়।
৯) শিশু ভীতি
শিশুদের ভয় পায় কুকুর;
শিশুদের ভয় পাওয়া কুকুরের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, একটি গৃহপালিত কুকুরকে যা শেখানো হয় সে তা-ই শেখে এবং যে পরিবেশে বড় হয়, তার সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর সে নতুন কিছু সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারে না। শিশুদের ব্যাপারটিও তেমন। হঠাৎ করে প্রভুর সংসারে নতুন সদস্যের আগমন সে সহজভাবে নিতে পারে না। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে বড় হওয়া একটি কুকুর আকার আকৃতিতে বেশ ছোট এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিমা করা একটি শিশুকে এমনিতেই ভয় পায়। অনেকসময় শিশুর আদরকেও সে নিজের জন্য হুমকি মনে করে। তাই, বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে কোনো শিশুকে প্রথমেই এর সাহচার্যে ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়। কেননা তাতে কুকুরটির আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়ে নিলে কুকুরের এই ভয় কেটে যায়।
১০) যন্ত্রপাতির ভয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে কুকুরটি;
যন্ত্রপাতির উপর কুকুরের ভয় জন্মানোটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন, ব্লেন্ডার কিংবা ট্রেডমিলের মতো যন্ত্রপাতির উপর নানা কারণেই কুকুরের ফোবিয়া সৃষ্টি হয়। এর কারণ এসব যন্ত্রের অদ্ভুত শব্দ এবং কার্যকরণ। কুকুরের এরকম ফোবিয়া স্বাভাবিক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিপদজনক হতে পারে। কোনোরূপ দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই এই ফোবিয়া কাটানো উচিৎ। সেটা হতে পারে পরিচর্যার মাধ্যমে কিংবা ডগ ট্রেনার এর সাহায্যে। তবে বাসায় যেকোনো নতুন যন্ত্র আনলে প্রথমেই তা চালু না করে কুকুরকে মানিয়ে নেয়ার সময় দিলে এই ফোবিয়া সহজেই কেটে যায়।

টেক ফোবিয়া: মানব মনে প্রযুক্তি বিষয়ক যত ভীতি
অনেকেই হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, মানুষের ফোবিয়ার বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়েনি প্রযুক্তিও। যে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের জীবন সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে, অসংখ্য অসম্ভবকে সম্ভব করা যাচ্ছে, এমনকি অদূর ভবিষ্যতে গোটা বিশ্বকেই নিজের আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে আসতে পারার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেই প্রযুক্তির ব্যাপারেও কিছু মানুষের ভয় ও আতঙ্কের শেষ নেই। মানুষের প্রযুক্তি বিষয়ক এসকল ভীতির নামই হলো 'টেক ফোবিয়া'।
হয়তো ভাবছেন, টেক ফোবিয়া হয়তো মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে একদমই নতুন কোনো সংযোজন। কিন্তু না, সেটি সম্পূর্ণ ভুল একটি ধারণা। বিগত কয়েক শতক ধরেই রয়েছে এর অস্তিত্ব। এমনকি সেই অষ্টাদশ শতকেও অস্তিত্ব ছিল 'টেকনোফোবিয়া' নামক একটি বিশেষ ফোবিয়ার, যার অর্থ হলো 'প্রযুক্তিগত প্রভাবের ব্যাপারে অস্বাভাবিক ভীতি কিংবা উদ্বিগ্নতা'।
টেকনোফোবিয়া শব্দটির প্রথম আগমন ঘটে শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮৪০) সময়। তখন থেকেই ইউরোপীয় শিল্প-কারখানায় মানুষের বিকল্প হিসেবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে কাজ হারিয়েছিল একদল তাঁতিও। তারা নিজেদেরকে পরিচয় দিত 'লডাইট' (The Luddites) হিসেবে। তারা এতটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন কলকারখানায় গিয়ে তারা তাঁতযন্ত্র ভেঙে ফেলতে শুরু করে। অবস্থা নাগালের বাইরে চলে গেলে, ইংরেজ আইনসভা বাধ্য হয় যন্ত্র-ধ্বংসকে সর্বোচ্চ সাজার আওতাভুক্ত অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিতে।
ওই সময়টাতেই টেকনোফোবিয়া শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে, আর যারা নতুন প্রযুক্তি বা কাজের ধরনকে ভয় পায় বা বিরোধিতা করে, তাদেরকে ডাকা হতে থাকে লডাইট নামে। তবে তখনকার দিনে যে ভীতিকে টেকনোফোবিয়া নাম দেয়া হয়েছিল, তার সাথে বর্তমানের টেক ফোবিয়াকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটেছে, এবং সেগুলোর একেকটি একেকভাবে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। সেই সকল ভীতির একটি সামষ্টিক রূপকে অভিহিত করা হয় টেক ফোবিয়া হিসেবে।
অবশ্য এখন আমরা সামগ্রিক টেক ফোবিয়া নিয়ে নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের টেক ফোবিয়া নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব। তাহলে পাঠক, চলুন আর দেরি না করে জেনে নিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত টেক ফোবিয়াগুলোর সম্পর্কে।
নোমোফোবিয়া
এটি হলো নিজের মোবাইল ফোন ছেড়ে থাকার ভয়। 'নোমো' শব্দটি মূলত 'নো মোবাইল' শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের পোস্ট অফিস এই বিশেষ ফোবিয়াটির নামকরণ করে। সেখানে কর্মরতদের মধ্যে যারা মোবাইল ব্যবহার করতো, তাদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্বেগে ভোগার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছিল। এবং শেষমেষ পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার পর দেখা যায়, তাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগটি আসলে মোবাইল ফোন হারানো নিয়েই। সাইকোলজি টুডে'র এক প্রতিবেদন মতে, আজকাল কলেজ শিক্ষার্থীদের মাঝে গোসল করতেও মোবাইল নিয়ে ঢোকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বয়ঃসন্ধিকালীন অনেক মোবাইল ব্যবহারকারীর দাবি, তারা নাকি প্রয়োজনে নিজেদের কনিষ্ঠ আঙুল বিসর্জন দিতেও রাজি, তবু তারা মোবাইল কাছছাড়া করবে না!
আজকাল আবার নোমোফোবিয়ারও বিভিন্ন নতুন শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয়েছে। যেমন- কিছুক্ষণ পরপর মোবাইল ফোন চেক করে দেখা যে নতুন কারো মেসেজ বা কল এলো কি না, এ প্রবণতাটি কমবেশি সবার মধ্যেই বিদ্যমান। আবার অনেকে অবসেসড থাকে তার মোবাইলের ব্যাটারি নিয়ে। হয়তো ১০০ শতাংশ চার্জ আছে মোবাইলে, তবু তাদের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করতে থাকে ভয়, "মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাবে না তো!" আর নোমোফোবিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ হলো মোবাইল হারিয়ে ফেলা বা চুরি যাওয়ার ভয়। অর্থাৎ, মোবাইলের থেকে কিছুক্ষণ দূরে থাকার ভয়টাই এক পর্যায়ে এতটা তীব্র হয়ে ওঠে যে, ব্যবহারকারীর মনে প্রতি মুহূর্তে বিরাজ করে মোবাইল হারিয়ে ফেলা বা চুরি যাওয়ার আতঙ্ক।
সাইবারফোবিয়া
কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যাপারেও অনেকের মনে অহেতুক ভয় কাজ করে, যার নাম হলো সাইবারফোবিয়া। এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষের মনে করে, যেহেতু তারা ইতোপূর্বে কখনো কম্পিউটার ব্যবহার করেনি, তাই এখনো তারা এ যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারবে না। এজন্য তারা সবসময় চেষ্টা করে কম্পিউটার থেকে দূরে থাকতে, এবং কর্মস্থল বা শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ দেয়া হলে সেটি এড়িয়ে যেতে। আর কেউ যদি নিতান্ত বাধ্য হয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে শুরু করেও, তার মধ্য মাথাব্যথা, দুর্বল অনুভব করা, মানসিক উদ্বেগ বেড়ে যাওয়া, মৃত্যুভীতি সৃষ্টি হওয়া, প্রচুর ঘাম হওয়া, মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। অর্থাৎ, যতক্ষণ তারা কম্পিউটারে কাজ করে, ক্রমাগত তাদের দেহ ও মনে অস্বস্তি খেলা করতে থাকে, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে তা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও ফেলে যায়।
টেলিফোনোফোবিয়া
এটি সরাসরি টেলিফোন যন্ত্রটির প্রতি ভীতি নয়, বরং টেলিফোনে কথা বলার প্রতি ভীতি। আজকাল অনেকের মধ্যেই এই ফোবিয়াটি দেখা যায়। তারা হয়তো সামনাসামনি খুব বন্ধুত্বপরায়ণ। এমনকি মেসেজেও লিখিতভাবে খুব ভালো করেই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একধরনের ভীতি কাজ করতে শুরু করে। তারা ভাবে, তারা হয়তো গুছিয়ে কথা বলতে পারবে না, যা বলতে চায় তা ঠিকভাবে বলতে পারবে না, কিংবা তাদের কথা শুনে অপর প্রান্তের মানুষটি তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে না, হাসবে, অথবা তার সমালোচনা করবে। এ কারণে অনেকে এমনকি রাইড বুকিং করা কিংবা খাবার অর্ডার দেয়ার মতো অতি সংক্ষিপ্ত ফোনকলও দিতে পারে না।
সেলফিফোবিয়া
বর্তমান সময়ে যার হাতেই একটি স্মার্টফোন আছে, তাকেই দেখা যায় সেলফি তথা নিজের ছবি নিজে তোলার চেষ্টা করতে। সেলফি তোলার এমন প্রবণতা রীতিমতো মহামারী আকার ধারণ করেছে। তবে মুদ্রার অপর পিঠে ভিন্ন চিত্রও কিন্তু রয়েছে। অনেকেই চায় সেলফির মাধ্যমে নিজের খুব সুন্দর কোনো ছবি তুলতে। কিন্তু যখন তাদের ছবি ভালো আসে না, কিংবা তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, তখন সেলফির প্রতি তাদের মনে একধরনের বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। তাই পরবর্তীতে আর কখনো তারা সেলফি তুলতে চায় না।
এক্সপেন্সিভটেকফোবিয়া
এর অর্থ হলো, কোনো প্রযুক্তির পেছনে অতিরিক্ত অর্থ খরচের ভীতি। বিশেষ করে সেই প্রযুক্তিটি যদি কেউ ভালোভাবে ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে সেটির মাধ্যমে পয়সা উসুল হবে না বরং টাকাগুলো জলে যাবে, এমন রক্ষণশীল চিন্তা করতে দেখা যায় অনেককেই। যেমন- শুরুতে অনেকেই কম্পিউটার বা মোবাইল ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে না। মানুষ ব্যবহার করতে করতে এগুলোর ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে উঠবে, এমনটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যারা একটু বেশিই মিতব্যয়ী, তাদের কাছে মনে হতেই পারে, "আমি তো কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি না। কেনার পর এটা এমনিই পড়ে থাকবে। তাহলে আমি কেন খামোকা এটার পেছনে এত টাকা খরচ করবো!" এমন ফোবিয়ার কারণে অনেকের পক্ষেই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খুব দামি কোনো প্রযুক্তির মালিকানা লাভ করা সম্ভব হয় না।
নোইন্টারনেটফোবিয়া
ইন্টারনেট কানেকশন হারিয়ে ফেলা বিষয়ক এই ফোবিয়াটি বোধহয় সকলেরই আছে। ধরুন, মেসেঞ্জারে প্রিয়জনের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন, কিংবা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দাপ্তরিক কাজ করছেন। এমতাবস্থায় যদি হুট করে ইন্টারনেট কানেকশন হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কেমন হবে? অবশ্যই খুব খারাপ হবে। আর তাই কেউই চায় না এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে। শহরের বাইরে যাওয়ার সময় অনেকের মনেই আশঙ্কা জাগে, যদি নেটওয়ার্ক ভালো না থাকে? আবার এখন যেহেতু গরমকাল চলছে, আর গরমকালে বারবার লোডশেডিং হয়, তাই ওয়াইফাই ব্যবহারকারীদের এক সার্বক্ষণিক উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়, "হুট করে লোডশেডিং হয়ে ইন্টারনেট কানেকশনটাও চলে যাবে না তো!"
লোরিমোফোবিয়া
সোফা কিংবা কাউচে বসে টিভি দেখতে দেখতে রিমোট কন্ট্রোলটি হারিয়ে ফেলেছেন কখনো? বাজি ধরে বলতে পারি, প্রত্যেকের জীবনেই এমন দুঃস্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা অবশ্যই এসেছে, যখন সে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চ্যানেল পাল্টাতে চেয়েছে কিন্তু রিমোট কন্ট্রোলটি বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে। আর যারা একটু বেশি অবসেসিভ, একবার এমন অভিজ্ঞতার শিকার হওয়ার পর পরবর্তীতে প্রতিবার টিভি দেখার সময় তাদের মনে আবারো রিমোট কন্ট্রোলটি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা জাগা খুবই সম্ভব। তাছাড়া আজকাল যেহেতু টিভি ছাড়াও এসি, সাউন্ড সিস্টেম, স্ট্রিমিং সার্ভিসসহ আরো অনেক কিছু দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেই রিমোট কন্ট্রোলের প্রয়োজন হয়, তাই লোরিমোফোবিয়াও ক্রমশ বেড়েই চলেছে।
ড্রোস্মার্টয়ফোবিয়া
এটি একটু অদ্ভুত ধরনের ফোবিয়া বটে, তবে অমূলক নয় মোটেই। বিশেষত যাদের অভ্যাস (কিংবা বদভ্যাস) রয়েছে টয়লেটে যাওয়ার সময়ও হাতে করে স্মার্টফোনটি নিয়ে যাওয়ার, তারা হয়তো সহজেই এই ফোবিয়াটির সাথে একাত্মতা অনুভব করতে পারবেন। টয়লেটে স্মার্টফোন নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময়টুকুতেও ফোনের পর্দায় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এদিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া শেষে কিছু বিশেষ কাজও করা আবশ্যক। তো, একসাথে দু'টি কাজ করতে গিয়ে যদি কোনোভাবে মনোযোগ সরে যায়, আর তখন ফোনটি হাত থেকে পিছলে কমোডের ভেতর পড়ে যায়? অনেককেই এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে, যে কারণে অন্যরাও এখন টয়লেটে গিয়ে ভয় পেতে থাকে, "এই বুঝি আমার ফোনটিও পড়ে গেল!" চাইলে এই ফোবিয়াটি থেকে কিন্তু খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। স্রেফ আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো- টয়লেটে ফোন নিয়ে না ঢোকা, কিংবা ঢুকলেও সেটি হাতে নিয়ে টিপতে থাকার বদলে নিরাপদ কোনো স্থানে রেখে দেয়া।
ফরমাসপাসফোবিয়া
পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়াটা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই আমরা নিজেদের বিভিন্ন আইডির পাসওয়ার্ড ভুলে ফেলি, এবং তারপর ফরগেট পাসওয়ার্ড দিয়ে, নতুন করে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দিই। কিন্তু যদি এমন হয় যে আমরা আমাদের মাস্টার পাসওয়ার্ডটিই হারিয়ে ফেলি? হতে পারে সেটি মোবাইলের লক পাসওয়ার্ড, মূল মেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড, কিংবা ঘরের দরজা খোলার পাসওয়ার্ড। এসব পাসওয়ার্ড একবার হারিয়ে ফেললে নিশ্চিতভাবেই আমাদেরকে প্রচুর বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, প্রচুর সময় ব্যয় করে অ্যাকাউন্ট বা ডিভাইসটি পুনরুদ্ধার করা যাবে বটে, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সেটি চিরতরে ডিজেবল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকেই যায়। তাই তো, প্রযুক্তির সাথে যাদের নিত্য বসবাস, তাদেরকে সবসময় মাস্টার পাসওয়ার্ড স্মরণে রাখার চ্যালেঞ্জও জয় করতে হয়। আর যারা সহজেই ভয় পায় বা উদ্বিগ্ন হয়, তারা ফরমাসপাসফোবিয়ার শিকার হয়।
ফরআন্সাকুয়েফোবিয়া
পাসওয়ার্ড ছাড়াও আজকাল আমাদেরকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য কিছু গোপন প্রশ্নের উত্তর স্মরণে রাখতে হয়। কিন্তু কখনো কখনো পাসওয়ার্ড মনে রাখার চেয়েও এই উত্তরগুলো মনে রাখা ঢের বেশি কঠিন। মনে করুন, আপনি কোথাও নতুন একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, যেটির নিরাপত্তা প্রশ্ন হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাওয়া হলো, আপনার প্রিয় বই কোনটি। আপনার হয়তো একাধিক প্রিয় বই আছে। তাড়াহুড়ায় প্রথম যেটির নাম মাথায় এসেছে, সেটিই আপনি উত্তর হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন পর সেই উত্তরটি ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর অনেকদিন পর যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনার প্রিয় বই কোনটি, তাহলে আপনি যে পূর্বোল্লিখিত বইয়ের নামটিই এবারও উত্তর হিসেবে দেবেন, তেমনটি তো না-ও হতে পারে। তাই আজকাল অনেককেই তাড়া করে বেড়ায় ফরআন্সাকুয়েফোবিয়া।
ফোমো (FOMO) অথবা 'ফিয়ার অব মিসিং আউট'
বর্তমান সময়ে এটিও খুব বড় একটি ফোবিয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে আমাদের অনেকের জীবনটাই যেন একটি খোলা বইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। আমরা প্রতিনিয়ত কী করছি, কী খাচ্ছি, কী পরছি, কোথায় যাচ্ছি, কার সাথে আড্ডা দিচ্ছি- সবকিছুর আপডেট দিতে থাকি ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে। এর মাধ্যমে আমরা একধরনের মানসিক শান্তি পাই বটে। কিন্তু কখনো এটিই হতে পারে চরম মানসিক অশান্তির কারণ। হয়তো আমার বন্ধুরা সবাই মিলে কক্সবাজার ঘুরতে গেছে। আমি যেকোনো কারণেই হোক যেতে পারিনি। এখন আমি ফেসবুকে ঢুকতেও ভয় পাচ্ছি। কারণ ফেসবুকে ঢুকলেই তাদের আনন্দ করার ছবি, পোস্ট ইত্যাদি আমার চোখে পড়বে, এবং তখন আমার কাছে মনে হবে আমি হয়তো খুব বড় কিছু মিস করছি। আবার আমার মনে আফসোসও হবে, কেন আমি গেলাম না। অর্থাৎ আমি একপ্রকার নিশ্চিত যে ফেসবুকে ঢুকলেই আমার মন খারাপ হয়ে যাবে, আর তাই আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব ফেসবুক থেকে দূরে থাকার। এই 'আমি' কিন্তু কেবল আমিই নই, আপনারাও বিভিন্ন সময় এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন, তা-ই নয় কি?

ফেসমোফোবিয়া: ভূতের ভয় থেকে জন্ম নেয়া এক ফোবিয়া
ভয়’ শব্দটির সাথে আমরা সকলেই কমবেশি জড়িয়ে আছি। বিভিন্ন অলৌকিক বা অশরীরী ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের ‘ভূতের ভয়’ নামক অনুভূতি আবর্তিত হয়। আত্মানির্ভর বা পারলৌকিক বিষয়ের উপর কোনো চলচ্চিত্র বা গল্প বইয়ের রেশ যখন মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যায়, তখন এক গা ছমছমের অনুভূতির জন্ম নেয়। কারো কাছে ব্যাপারখানা নিতান্তই রোমাঞ্চের, আবার কারো কাছে জীবন কেড়ে নেয়ার মতো হুমকিস্বরূপ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অলৌকিক বা ভূতের অতিরিক্ত ভয়কে এক ধরনের ফোবিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার নাম ‘ফেসমোফোবিয়া‘।
ফেসমোফোবিয়া কী?
আপনি হয়তো খুব ভয়ের একটি চলচ্চিত্র দেখলেন বা একটা ভূতের বই পড়লেন। কিন্তু গল্প শেষ হয়ে গেলেও গল্পের চরিত্রগুলোর সাথে অনেক বেশি একাত্ম হয়ে আছেন। গল্পের চরিত্রগুলো এতটাই জীবন্ত ছিল যে চরিত্রগুলো যেন কল্পনা থেকে বাস্তবে উঠে এসেছে। আর মনের অজান্তেই নিজের চারপাশে এক ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে নিয়েছেন।
রাতে যখন ঘুমোতে গেলেন, তখন গল্পের সবগুলো ভৌতিক দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। বিছানায় একা শুয়ে আছেন, কিন্তু মনে হলো কীসের যেন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। দরজায় কেমন যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে। ঘরের কাঠের আসবাব থেকে ঘুনে ধরার আওয়াজ আসছে। মাথার কাছে রাখা ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ।
জানলার পর্দাটা খোলা ছিল বলে বাইরের ল্যাম্পপোস্টের কিছুটা আলো ঘরে ঢুকে পড়েছে। আধো আলো ছায়াতে বিছানার পাশেই যেন কারো অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে রাখতে চাইছেন, তবু কেন জানি চোখ খুলে ফেলছেন বারবার। শরীরের উপর চাদরটা দিয়ে মুখটা ভালোভাবে ঢেকে দিলেন, কিন্তু মনে হতে লাগলো কেউ একজন যেকোনো সময় চাদরটি মুখ থেকে সরিয়ে নিবে। আবার বিছানার পাশেই হয়তো গল্পের সেই সাদা মুখের বাচ্চাটি গুটি দিয়ে বসে আছে।
চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই, তবুও চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না। চোখ খুললেই হয়তো লাল শাড়ি পরা মেয়েটিকে দেখা যাবে, যে কিনা রাতের আঁধারে এসেই গলা টিপে দিয়ে যেত। চাইলেই বৈদ্যুতিক বাতিটি জ্বালিয়ে কিছুটা হলেও ছাড় পাওয়া যায় কিন্তু সকালেই নিন্দুকের টিপ্পনি সইতে হবে। ভীতু নামটা যেন কিছুতেই গায়ে মাখা যায় না।
হঠাৎ করেই কীসের যেন একটা আওয়াজ হলো বা ঘরের জানালাটা নড়ে উঠল। আপনিও হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন। যে যা-ই বলুক, এভাবে তো আর থাকা যায় না। এভাবে চলতে থাকলে ভয়েই দম বন্ধ হয়ে আসবে। উঠে গিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন বাতি, আর বাকিটা রাত কিছুটা ঘুম আর কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। কারো কারো ক্ষেত্রে ভূতের ভয় এমনই তীব্র আকার ধারণ করে যে নিদ্রাহীনতা, হৃদরোগ, স্কিজোফ্রেনিয়া, ইনসোমনিয়ার মতো রোগেও আক্রান্ত হতে পারেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ভূতের এই ভয়কেই ফেসমোফোবিয়া বলে আখ্যা দেয়া হয়।
ভূতের ভয় অনেক মানসিক ব্যাধির কারণ হয়ে উঠতে পা
লক্ষণসমূহ
ভূতের ভয় কমবেশি আমাদের সকলের মনের মধ্যে রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হলো ছোটবেলা থেকেই আমরা বড়দের কাছ থেকে ভূত-প্রেত, রূপকথা শুনে বড় হই। তাই ভূত সম্পর্কিত একধরনের অদৃশ্য ভয় আমাদের বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। অনেকের মনের মধ্যে ভূতের ভয় থাকলেও তা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন।
তবে ফেসমোফোবিয়ায় আক্রান্ত, তাদের ক্ষেত্রে ভয়ের মাত্রাটি অনেক বেশি। তারা একা ঘরে থাকতে ভয় পায়, অন্ধকারকে অসম্ভব ভয় পায়, নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারে না, শহরে বাস করলে গ্রামে কোনভাবেই রাত কাটাতে চায় না, ভৌতিক গল্প, সিনেমা বা ছবি থেকে অনেক দূরে থাকেন। তবে এই ধরনের ফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকেন।
১। একা ঘুমুতে ভয় পান
২। পুরোপুরি অন্ধকার ঘরে ঘুমুতে চান না
৩। মনের মধ্যে সবসময় অলীক ভূতের ছবি ভাসতে থাকে
৪। যেকোনো পরিস্থিতিতে ভূতের অস্তিত্বের আভাস পান
৫। মাঝে মাঝে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন
৬। সবসময় মুখে চিন্তার ছাপ দেখা যায়
৭। নিদ্রাহীনতায় ভুগতে থাকেন কারণ ভূতের ভয়ে ঘুমুতে পারেন না
৮। বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি অনেক বেশি আসক্তি হয়ে পড়েন
করণীয়
ভূতের ভয়কে সাধারণত খুব বেশি উদ্বেগজনক বলে মনে করা হয় না। তবে ভয়ের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে অথবা এই ভয় যদি দৈনন্দিন জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলে, তবে এই বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। তবে প্রথমেই উদ্বিগ্ন না হয়ে নিজে থেকেই চেষ্টা করতে হবে এই ফোবিয়া থেকে বের হয়ে আসার।
ভয়কে জয় করার চেষ্টা
ফেসমোফোবিয়া থেকে মুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো ভূতের ভয় মন থেকে পুরোপুরি বের করে ফেলার চেষ্টা করা। ভূতের ভয়কে যত বেশি প্রশ্রয় দেয়া হবে, ভয় ততই মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাবে। তাই সর্বপ্রথম নিজের মনকে বোঝাতে হবে, ভূত বলে কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ নিজের মনের ভুল ধারণা। আর যদি আপনি ভূতে বিশ্বাস করে থাকেন, তবে চেষ্টা করতে হবে ভূতের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করা। কারণ আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে ভূত যদি থেকেও থাকে, তা কখনো সরাসরি আপনাকে আঘাত করতে পারবে না, বরং একমাত্র ভয়ই হয়ে উঠতে পারে আপনার মৃত্যুর কারণ। তাই মনকে শক্ত করে ভূতের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে মনকে গড়ে তুলুন।
মনকে অনেক বেশি যৌক্তিক করে তোলা
বিজ্ঞানের এই যুগে ভূতে বিশ্বাস রাখা খুব কষ্টসাধ্য। তবুও যদি মনের মধ্যে ভূতের ভয় বাসা বাঁধে, তবে মনের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাকে জাগ্রত করে তুলুন। কোনো কিছুর প্রমাণ ছাড়া সহজেই মেনে নেয়ার অভ্যাস দূর করতে হবে। কোনোকিছু দেখে বা অনুভব করে অথবা শব্দ শুনে ভয় পেলে তার উৎসের সন্ধান করতে হবে। কী কারণে এমন ঘটল, তা বের করলে সব কৌতূহলের সমাধান হয়ে যাবে।
ভয় থেকে মুক্তির জন্যে কৌতুকের আশ্রয় নিন
ভূতের ভয় পাচ্ছেন দেখে নিজেকে নিয়ে কৌতুক করুন। অথবা আপনার খুব পছন্দের কোনো কৌতুক চরিত্রের কথা চিন্তা করুন। নিজের জীবনের মজার কিছু স্মৃতি নিয়ে ভাবুন। ভূত সবসময় খারাপ হয় না, ভালোও হতে পারে এমন চিন্তা মাথায় আনুন। এর একটি ভালো উদাহরণ ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ এর ভূতের অবয়ব।
নিজেকে নিরাপদ রাখা
অনেক কিছু করেও যদি ভূতের ভয় জয় করতে না পারেন, তবে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাধারণত কোনো ভূতের চলচ্চিত্র দেখলে বা বই পড়লে এমনটা মাথার মধ্যে বেশি কাজ করে, যা কয়েকদিনের মধ্যে এমনিতেই মিলিয়ে যায়। তাই যদি খুব বেশি ভয় মনের মধ্যে গেঁথে যায় তবে রাতে কারো সাথে ঘুমান, অথবা বাতিটা জ্বালিয়ে রাখুন কিংবা হালকা কোনো গান চালিয়ে রাখুন।
ভূতের চলচ্চিত্র দেখা বা বই পড়া থেকে বিরত থাকা
যাদের ভূতের ভয় খুব বেশি, তারা চাইলে ভূতের চলচ্চিত্র দেখা অথবা ভূতের বই পড়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। তবে অনেকেই ভয় পেলেও ভূতের চলচ্চিত্র দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত একা থাকার প্রবণতা কম দেখা যায়। অন্যথায় রাতের বেলা ভূতের চলচ্চিত্র না দেখে দিনের বেলা দেখে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভূতের ভয় পাওয়ার আনন্দটাও ষোলোআনায় যে হারাতে হবে, তা বলাই বাহুল্য।
মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া
অনেকেই ভূতের ভয়ে এত বেশি আক্রান্ত হয়ে পড়েন, যার কারণে তাদের দৈনন্দিন জীবন অনেক বেশি ব্যাহত হয়ে থাকে। এই ধরনের ফোবিয়া থেকে মানসিক আরো জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ভূতের ভয়ের ফোবিয়া অল্পতেই বিনষ্ট করে নেয়া উচিত। কোনোভাবেই যদি ভূতের ভয় কমানো না যায় এবং এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে থাকে, তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।
বিজ্ঞানের এই যুগে ভূতের ভয় একধরনের বিলাসিতা বা বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সত্যটি যাদের মনে গেঁথে রয়েছে, তাদের ভূতের বিষয়টি আনন্দ ও নিছক বিনোদনের একটি বিষয়। অনেকের মতে, ভয় না পেলে ভূতের চলচ্চিত্র বা বই পড়ে লাভটাই বা কী? তবে মানুষের মন বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন হয়ে উঠতে পারে। তাই এই ফোবিয়াকে সবসময় ছোট করে দেখা উচিত নয়। ফোবিয়া খুব তীব্র হয়ে উঠলে এর উপযুক্ত চিকিৎসা নেয়া মোটেও লজ্জার চোখে দেখা উচিত নয়।

আরাকনোফোবিয়া: মানুষ কেন মাকড়শাকে ভয় পায়
অনেকেই হয়তো “ব্যাপারটি নারীদের সাথে বেশি ঘটে থাকে”- এমনটা বলবেন। তবে গবেষণানুসারে, নারীদের প্রতি তিনজনে একজন এবং পুরুষদের গড়ে প্রতি চারজনে একজন এই সমস্যায় ভুগে থাকেন। বলছিলাম আরাকনোফোবিয়ায় কথা। বাংলায় যার সহজ নাম মাকড়শা থেকে ভয়। আরাকনোফোবিয়ায় আক্রান্তরা মাকড়শা নামক ছোট্ট এবং অতি সাধারণ প্রাণীকে নিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে ভুগে থাকেন। যার উদাহরণ হয়তো আপনি নিজেই! কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতকিছু থাকতে আমরা মাকড়শাকে কেন ভয় পাই? এমনকি, মাকড়শা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জেনেও এটি দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাই। কিন্তু কেন? আরাকনোফোবিয়া কেন হয়?
ফোবিয়া মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলো হল- অ্যাগ্রোফোবিয়া বা ঘরের বাইরে যাওয়ার ভয়, সোশ্যাল ফোবিয়া বা সামাজিকতায় ভয় এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে ভয়। মাকড়শা নিয়ে আপনার ভয়টি শেষ রকমের ফোবিয়া বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে ফোবিয়ার মধ্যে পড়ে। তাহলে কি আপনার সাথে মাকড়শা নিয়ে এর আগে কোনো বাজে ঘটনা ঘটেছিল? সবার সাথেই কি তা-ই হয়েছে? প্রশ্ন জাগতেই পারে আপনার মনে। তবে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। আরাকনোফোবিয়া বা মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার এই ব্যাপারটি মানুষের মধ্যে এখন জন্ম নেয়নি। আপনি এবং বাকি সব মানুষ যে মাকড়শাকে ভয় পায়, সেটি মোটেও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয়। এর পেছনে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের হাত। একটা সময় আমাদের প্রাচীন মানবদের কাছে না ছিল বড় হাতিয়ার, আর না ছিল কোনো উন্নত ওষুধ। আরাকনোফোবিয়ার উৎপত্তি তখন থেকে। নির্দিষ্ট এই গোত্রের প্রাণীদের কাছ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকতো তখন মানুষের। তাদেরকে প্রতিহত করার কোনো উপায় জানা ছিল না কারো। সেইসাথে আক্রমণের পর ব্যবহার করার মতো ঔষধ ছিল না তাদের কাছে। ফলে এই আক্রমণে মারা যেত অনেক মানুষ।
সেখান থেকেই মাকড়শা গোত্রের যেকোনো প্রাণীর প্রতি আমাদের স্বভাবজাত ভয়ের জন্ম। বর্তমানে আমার কিংবা আপনার সাথে মাকড়শা সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটুক কিংবা না ঘটুক, ভয় পাওয়াটা তাই হয়ে পড়ে স্বাভাবক একটি ব্যাপার। মাকড়শা সম্পর্কে তো জানা হল। কিন্তু মাকড়শা কেবল তার গোত্রের একমাত্র প্রাণী নয়। আরো অনেকে আছে তার সাথে। প্রাচীনকালে কেবল মাকড়শা নয়, বরং এই গোত্রের সব প্রাণীকেই ভয় পেত মানুষ। আরাকনিড একটি প্রাণীগোষ্ঠী। এই গোত্রের মধ্যে আছে মাকড়শা, বিছেসহ আরো অনেক প্রাণী, যাদের শরীর দেখতে অনেকটা একইরকম। আর এদের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে আরাকনোফোবিয়া হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটির গ্রাহাম ডেভি এই সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা চালান। এতে তার সাথে অংশ নেয় ১১৮ জন শিক্ষার্থী। আর সেখান থেকে পরীক্ষায় জানা যায় যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ মাকড়শা এবং আরাকনিড গোত্রের প্রাণীদেরকে ভয় পায়। আর এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী।
তবে প্রশ্ন থাকে যে, মানুষ কি কেবল এই একটি কারণেই মাকড়শাকে ভয় পায়? একদম নয়। মানুষের মাকড়শার প্রতি এই ভয় জন্ম নেওয়ার পেছনে আছে তার পরিবারের প্রভাব। পরীক্ষায় জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তি মাকড়শাকে প্রচন্ড পরিমাণে ভয় পান তাদের পরিবারেও কারো না কারো ঠিক একই সমস্যা ছিল। তবে কারো উপরে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে জিনগত কোনো ব্যাপার বেশি প্রভাব রাখে নাকি পরিবেশগত, সেটি খুব একটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। আশ্চর্যজনকভাবে, মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার দিকে সবচাইতে এগিয়ে থাকে শিশুরা। বিভিন্ন শিশুকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাদের ভয়ের কারণ হিসেবে গাড়ি, নিঃশ্বাস না নিতে পারা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো উল্লেখ করেছে তারা। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ এবং সবচাইতে এগিয়ে থাকা ভয় প্রাধান্য পেয়েছে। আর সেটি হলো মাকড়শাকে ভয়। মাকড়শাকে ভয় পাওয়া বা আরাকনোফোবিয়ার সাথে যে আমাদের প্রাচীন মানবদের সম্পর্ক আছে, তা তো আগেই উল্লেখ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আরো বেশি পরিষ্কার ধারণা পেতে ডেভির গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গবেষণা চালানো হয় জানার চেষ্টা করা হয় যে পরিবেশ নাকি জিন- কোনটা প্রভাব রাখে এই ক্ষেত্রে?
স্বাস্থ্য
আরাকনোফোবিয়া: মানুষ কেন মাকড়শাকে ভয় পায়?
অনেকেই হয়তো “ব্যাপারটি নারীদের সাথে বেশি ঘটে থাকে”- এমনটা বলবেন। তবে গবেষণানুসারে, নারীদের প্রতি তিনজনে একজন এবং পুরুষদের গড়ে প্রতি চারজনে একজন এই সমস্যায় ভুগে থাকেন। বলছিলাম আরাকনোফোবিয়ায় কথা। বাংলায় যার সহজ নাম মাকড়শা থেকে ভয়। আরাকনোফোবিয়ায় আক্রান্তরা মাকড়শা নামক ছোট্ট এবং অতি সাধারণ প্রাণীকে নিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে ভুগে থাকেন। যার উদাহরণ হয়তো আপনি নিজেই! কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতকিছু থাকতে আমরা মাকড়শাকে কেন ভয় পাই? এমনকি, মাকড়শা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জেনেও এটি দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাই। কিন্তু কেন? আরাকনোফোবিয়া কেন হয়?
মাকড়শার ভয় বা আরাকনোফোবিয়া;
এই ‘কেন’র উত্তর জানতে হলে আমাদের জানতে হবে ফোবিয়া কী। ফোবিয়া মূলত ভয়। না, সাধারণ কোনো ভয় নয়। বেশ জাঁকিয়ে বসা ভয়। পরীক্ষায় ভালো না লিখে আসলে ফলাফল দেওয়ার সময় আপনার দুশ্চিন্তা এবং ভয় হতেই পারে। তবে ফোবিয়া ঠিক সেরকম ভয় নয়। এটি একজন মানুষের মধ্যে অনেকটা পাকাপাকিভাবে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় বাস করে। মাকড়শার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটা একই রকম। আশেপাশে কোনো মাকড়শা নেই, থাকলেও সেটি আপানাকে কোনোভাবেই আঘাত করতে পারবে না। সুতরাং এই ছোট্ট প্রাণীকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই। এতকিছু জানার পরেও যদি আপনাকে কেউ বলে বসে- ঐ যে মাকড়শা! আর আপনি অসম্ভব ভয় পান, তাহলে সেটা সাধারণ ভয়ের পর্যায়ে থাকে না। এই ভয়কে আমরা এত বেশি নিজেদের মধ্যে পুষে রেখেছি যে, এটি খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যতজন মানুষই কোনো ফোবিয়া বা ভীতির ভুক্তভোগী হয়ে থাকুন না কেন, সেটি শেষ পর্যন্ত ফোবিয়াই থাকে। আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ফোবিয়া কেন হয়? প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সহজ নয়। ঠিক কী কারণে ফোবিয়া হয়ে থাকে সেটা এখনো পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। তবে অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা হতে পারে আপনার কোনো ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কারণ। তবে কিছু ফোবিয়া বা ভীতি আছে যেগুলো মানুষ জন্ম থেকেই সাথে নিয়ে আসে। আর সেগুলো হচ্ছে- উচ্চতা থেকে ভয়, অন্ধকারে ভয়, চলন্ত বস্তুতে ভয় ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই ভয়গুলো কাজ করে। আর বাকি ফোবিয়া বা ভীতিগুলোকে অর্জিত ফোবিয়া বলে। যেগুলো মানুষ আগে থেকে নয়, বরং জন্ম নেওয়ার পর শেখে।
মাকড়শার প্রতি মানুষের এই ভয় আজকের নয়; Source: San Diego Zoo Animals
ফোবিয়া মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলো হল- অ্যাগ্রোফোবিয়া বা ঘরের বাইরে যাওয়ার ভয়, সোশ্যাল ফোবিয়া বা সামাজিকতায় ভয় এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে ভয়। মাকড়শা নিয়ে আপনার ভয়টি শেষ রকমের ফোবিয়া বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে ফোবিয়ার মধ্যে পড়ে। তাহলে কি আপনার সাথে মাকড়শা নিয়ে এর আগে কোনো বাজে ঘটনা ঘটেছিল? সবার সাথেই কি তা-ই হয়েছে? প্রশ্ন জাগতেই পারে আপনার মনে। তবে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। আরাকনোফোবিয়া বা মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার এই ব্যাপারটি মানুষের মধ্যে এখন জন্ম নেয়নি। আপনি এবং বাকি সব মানুষ যে মাকড়শাকে ভয় পায়, সেটি মোটেও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয়। এর পেছনে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের হাত। একটা সময় আমাদের প্রাচীন মানবদের কাছে না ছিল বড় হাতিয়ার, আর না ছিল কোনো উন্নত ওষুধ। আরাকনোফোবিয়ার উৎপত্তি তখন থেকে। নির্দিষ্ট এই গোত্রের প্রাণীদের কাছ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকতো তখন মানুষের। তাদেরকে প্রতিহত করার কোনো উপায় জানা ছিল না কারো। সেইসাথে আক্রমণের পর ব্যবহার করার মতো ঔষধ ছিল না তাদের কাছে। ফলে এই আক্রমণে মারা যেত অনেক মানুষ।
সেখান থেকেই মাকড়শা গোত্রের যেকোনো প্রাণীর প্রতি আমাদের স্বভাবজাত ভয়ের জন্ম। বর্তমানে আমার কিংবা আপনার সাথে মাকড়শা সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটুক কিংবা না ঘটুক, ভয় পাওয়াটা তাই হয়ে পড়ে স্বাভাবক একটি ব্যাপার। মাকড়শা সম্পর্কে তো জানা হল। কিন্তু মাকড়শা কেবল তার গোত্রের একমাত্র প্রাণী নয়। আরো অনেকে আছে তার সাথে। প্রাচীনকালে কেবল মাকড়শা নয়, বরং এই গোত্রের সব প্রাণীকেই ভয় পেত মানুষ। আরাকনিড একটি প্রাণীগোষ্ঠী। এই গোত্রের মধ্যে আছে মাকড়শা, বিছেসহ আরো অনেক প্রাণী, যাদের শরীর দেখতে অনেকটা একইরকম। আর এদের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে আরাকনোফোবিয়া হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটির গ্রাহাম ডেভি এই সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা চালান। এতে তার সাথে অংশ নেয় ১১৮ জন শিক্ষার্থী। আর সেখান থেকে পরীক্ষায় জানা যায় যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ মাকড়শা এবং আরাকনিড গোত্রের প্রাণীদেরকে ভয় পায়। আর এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী।
পুরুষদের চাইতে নারীরা মাকড়শাকে বেশি ভয় পায়; Source: Medical News Today
তবে প্রশ্ন থাকে যে, মানুষ কি কেবল এই একটি কারণেই মাকড়শাকে ভয় পায়? একদম নয়। মানুষের মাকড়শার প্রতি এই ভয় জন্ম নেওয়ার পেছনে আছে তার পরিবারের প্রভাব। পরীক্ষায় জানা যায় যে, যেসব ব্যক্তি মাকড়শাকে প্রচন্ড পরিমাণে ভয় পান তাদের পরিবারেও কারো না কারো ঠিক একই সমস্যা ছিল। তবে কারো উপরে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে জিনগত কোনো ব্যাপার বেশি প্রভাব রাখে নাকি পরিবেশগত, সেটি খুব একটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। আশ্চর্যজনকভাবে, মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার দিকে সবচাইতে এগিয়ে থাকে শিশুরা। বিভিন্ন শিশুকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাদের ভয়ের কারণ হিসেবে গাড়ি, নিঃশ্বাস না নিতে পারা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো উল্লেখ করেছে তারা। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ এবং সবচাইতে এগিয়ে থাকা ভয় প্রাধান্য পেয়েছে। আর সেটি হলো মাকড়শাকে ভয়। মাকড়শাকে ভয় পাওয়া বা আরাকনোফোবিয়ার সাথে যে আমাদের প্রাচীন মানবদের সম্পর্ক আছে, তা তো আগেই উল্লেখ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আরো বেশি পরিষ্কার ধারণা পেতে ডেভির গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গবেষণা চালানো হয় জানার চেষ্টা করা হয় যে পরিবেশ নাকি জিন- কোনটা প্রভাব রাখে এই ক্ষেত্রে?
মাকড়শা এবং শিশু; Source: founditgood.com
২০০৩ সালে জন হেত্তেমা ভার্জিনিয়া ইন্সটিটিউট ফর সাইকায়াট্রিক এন্ড বিহেভিওরাল জেনেটিক্স থেকে তার সহকর্মীদের নিয়ে শুরু করেন এই গবেষণা। এই গবেষণায় তারা ব্যবহার করেন জমজদের উপরে। এই জমজ শিশুদেরকে সম্পূর্ণ দু’ভাবে বড় করা হয়। পরিবেশ আলাদা দেওয়া হয় এবং এটা নিশ্চিত করা হয় যে তাদের মধ্যে একজন মাকড়শা দেখেনি আর মাকড়শার সাথে তার কোনোরকম বাজে কোনো অভিজ্ঞতাও হয়নি। পরীক্ষা চলতে থাকে। খানিকটা বড় হওয়ার পর তাদের দুজনকেই মাকড়শার ছবি দেখানো হয়। আর ফলাফল? মাকড়শা দেখুক কিংবা না দেখুন, মাকড়শার সাথে বাজে অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক- এরা দুজনেই ভয় পেয়ে যায় মাকড়শার ছবি দেখে। আর সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসেন গবেষকেরা যে, আরাকনোফোবিয়া কোনো পরিবেশগত সমস্যা নয়। পরিবেশের উপরে কিংবা নিজের অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে এই ভয়কে ধারণ করতে হয় না মানুষের। মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার এই ফোবিয়া জন্ম থেকে নিজের সাথে নিয়ে আসা এবং শেখা- এই দুটোর মাঝখানে পড়ে যায়। তাহলে, কী ভাবছেন? আপনারও আছে নাকি আরাকনোফোবিয়া?

অ্যালোডক্সাফোবিয়া: মতামত শোনার ফোবিয়া
আপনাকে যদি কেউ নিজের মতামত জানায় কিংবা আপনার বিশ্বাসের বিপরীতে কিছু বলে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে? কেউ কেউ ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করে বোঝার চেষ্টা করবেন যে কার কথা ঠিক। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছেন, যারা নিজেদের মতামতকে কোনো বাছবিচার ছাড়াই ঠিক ধরে নেন এবং বাকিদের কথাকে পাত্তাও দেন না। বিষয়টি কে কীভাবে নেবে, সেটা তার উপরই নির্ভর করে। তবে অন্য কারো মতামত শুনে ভয় পাওয়ার বিষয়টি নিতান্তই অস্বাভাবিক। একটি কাজ করলে কে কী বলবে বা একটি বিষয়ে আপনার মত শুনে বাকিদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা আমরা সকলেই কম-বেশি চিন্তা করি। কিন্তু এই চিন্তা এবং ভয়ের মধ্যে রয়েছে বিশাল পার্থক্য। এই ভয়ের মানে হলো আপনার একধরনের ফোবিয়া রয়েছে। অন্যের মতামত শোনার ফোবিয়া, যাকে বলা হয় ‘অ্যালোডক্সাফোবিয়া’।
‘অ্যালোডক্সাফোবিয়া’-এর উৎপত্তি ‘ডক্সাফোবিয়া’ থেকে হলেও দুটি শব্দ অর্থগত দিক থেকে পরস্পরের বিপরীত। ডক্সাফোবিয়া হলো মতামত ‘প্রকাশ’ করার ভয়। অন্যদিকে ‘অ্যালোডক্সাফোবিয়া’ মানে অন্য কারো মতামত ‘শোনার’ বা ‘জানার’ ভয়। তিনটি গ্রিক শব্দ ‘অ্যালো’, ‘ডক্স’ এবং ‘ফোবোস’ থেকে এই ফোবিয়ার নামটির উদ্ভব। উল্লেখ্য, ‘অ্যালো’ অর্থ ভিন্ন, ‘ডক্স’ হলো মতামত এবং ‘ফোবোস’ বলতে ভয়ের দেবতাকে বোঝানো হয়। ফোবিয়ার বিষয়টা হলো নির্দিষ্ট কোনো একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে কারো অবাধ ভয়। সেই ব্যাপারে ভয় পাওয়াটা ভিত্তিহীন কিংবা অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও তা কাটিয়ে উঠতে না পারা। ফলস্বরূপ, ফোবিয়ার শিকার ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
অ্যালোডক্সাফোবিয়া যাদের মধ্যে রয়েছে, তারা বাকিদের মতামত শোনার ভয়ে নিজেদের উপর নিজেরাই অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করে বসে। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই ফোবিয়া। মতামত শোনার বা জানার ভয়ের বিষয়টা শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট বয়সের মানুষদের জন্য নয়। বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও শিকার হতে এই ফোবিয়ার। কোমল শিশুদের মনেও ভয় জাগতে পারে, অন্যরা কী ভাববে তা ভেবে। আর এই অযৌক্তিক ভয় তাদের মনে শক্ত করে ঘর বেঁধে বসে। যেমন- পরীক্ষায় তাদের ফলাফল দেখলে বাকিরা কী বলবে কিংবা নিজেকে অন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট ও অদক্ষ মনে করে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করা।
অথবা হেরে গেলে বাকিরা সমালোচনা করবে, তা ভেবে ভিত্তিহীন ভয় পাওয়া। বড়দের ক্ষেত্রেও এরকম ভয় লক্ষ্য করা যায়। এই পোশাক পরলে বাকিরা কী বলবে, এই উত্তরটা এভাবে বললে সবাই তার সম্পর্কে কী ভাববে কিংবা এমনিতেই সারাক্ষণ অকারণে তার সম্পর্কে কে কী ভাবছে তা নিয়ে চিন্তা করা বা মতামতটা জেনে ফেলার যে ভয় সেগুলোই অ্যালোডক্সাফোবিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ধীরে ধীরে এই ভীতি তাদের চেতনাশক্তিকে কবজ করে ফেলে। এতে করে তারা পরবর্তীতে নিজের মতো করে কোনো কিছু করার বা মত প্রকাশের সাহস পায় না। অ্যালোডক্সাফোবিয়া একধরনের বিরল এবং অস্বাভাবিক সামাজিক ফোবিয়া। এই ধরনের ফোবিয়া ভুক্তভোগীকে সমাজ থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তার জীবনের, বিশেষ করে পেশাগত জীবনের ক্ষতি করে থাকে।
অ্যালোডক্সাফোবিয়ার কারণ
ফোবিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিই সাধারণত নিজেদের ভয়-ভীতির কথা বলতে চায় না। তা-ও কিছু কিছু মানুষ নিজেদের ভয়ের পেছনের কারণ জানান। এক্ষেত্রে মূলত অতীতের কোনো খারাপ ও আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা দায়ী বলে জানা যায়। সবচাইতে দুঃখজনক বিষয় হলো মা-বাবা, শিক্ষক কিংবা পরিচিত জনের কারণেই মূলত উঠতি শিশুদের এই ফোবিয়ার সৃষ্টি হয়। সবসময় বা অতিরিক্ত খবরদারি বা সমালোচনা করলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে একজন ব্যক্তির উপর। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবহারের ফল হিসেবে মাঝে মাঝে অ্যালোডক্সাফোবিয়া লক্ষ্য করা যায়।
কৌতূহলশূন্য এবং অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি, যারা সমালোচনা এবং প্রতিশোধের মতো বিষয়গুলোর প্রতি ভীত থাকে, তাদেরকেই এই ফোবিয়ার ভোগান্তিতে পড়তে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এসব অপ্রিয় অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের একটি অংশ এমিগডালায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে যেকোনো চাপে বা সমস্যায় পড়লে মস্তিষ্ক একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। এজন্য একজন ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ রাখতে নিজের অজান্তেই অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকা শুরু করে, যাতে করে অন্য কারো মতামত শোনা না লাগে।
যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা সামাজিক মাধ্যমও মতামত জানার এই ফোবিয়াকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন- খবরের কাগজ, টেলিভিশন এবং যেকোনো সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হওয়া যেকোনো মন্দ খবর অ্যালোডক্সাফোবিয়ার রোগীর জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার অনেক সময় এই ফোবিয়ার পেছনে দায়ী থাকে কোনো বংশগত ফ্যাক্টর বা জেনেটিক সমস্যা।
অ্যালোডক্সাফোবিয়ার লক্ষণসমূহ
এই ফোবিয়া হলে একজন ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণ দেখা যায়। অ্যালোডক্সাফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবস্থা কারো মতামত শুনলে এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে এর ফলে সেই ব্যক্তি প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হতে পারে। আর মতটা যে সবসময় নেতিবাচক হয় তা-ও না। ইতিবাচক কোনো কথা শুনেও চটে যেতে পারে এই ফোবিয়ার শিকার কোনো ব্যক্তি। এর কিছু সাধারণ লক্ষণ হলো ঘন ঘন হাত ঘামানো, অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, বমি বমি ভাব এবং অকারণেই অসুস্থতা অনুভব করা।
এই ধরনের ফোবিয়া হলে রোগী ভালো বা খারাপ নির্বিশেষে সব রকমের মতামত শুনলেই রেগে যায়। অথবা এর উল্টোটাও হতে পারে। কারো কথা শুনতে হবে বা কেউ কি ভাবছে তা জানা লাগবে বলে কিছু অ্যালোডক্সাফোবিক ব্যক্তি সেসব স্থানে যাবেই না, যেখানে মত প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকতে পারে। অর্থাৎ সামাজিক জীবনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এই ফোবিয়া। আর এতে করে অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে এবং জীবনের ভালো সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের মধ্যে অনিরাপত্তা এবং আত্মসম্মানবোধের অভাবও লক্ষ্য করা যায়। একটি জরিপে দেখা যায়, ১৮ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে অ্যালোডক্সাফোবিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ১৮-৩৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রেও রোগীদের সংখ্যা অনেক। সাধারণত নারীরা এই ফোবিয়ার শিকার বেশি হয়।
প্রতিকার
অ্যালোডক্সাফোবিয়ার কারণ জানা গেলে একজন ডাক্তার রোগীকে তার সমস্যা বা রোগ সেরে উঠতে সহায়তা করতে পারে। এর জন্য ব্যবহৃত থেরাপিগুলোর মধ্যে রয়েছে টক থেরাপি, সাইকোথেরাপিউটিক কাউন্সেলিং, গ্রুপ থেরাপি, সিস্টেমিক ডিসেন্টিসাইজেশন, হিপনোথেরাপি ইত্যাদি। এছাড়া অ্যালোডক্সাফোবিয়া কাটিয়ে তোলার সবচাইতে বড় অন্তরায় হলো রোগী নিজে থেকে প্রথমেই চিকিৎসা নিতে রাজি হন না। তবে এই সমস্যা সমাধানের তাগিদে রোগীর যথাযথ সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন যার জন্য পরিবারের সদস্যরা মূলত কাজ করতে পারে। একজন ফোবিককে নিজের সমস্যা বলার জন্যে উৎসাহিত করা উচিত। কেননা, অসুবিধা না বললে কখনো কারো সাহায্য করা সম্ভব নয়। অ্যালোডক্সাফোবিক ব্যক্তি প্রতিদিন তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও মতামত পরিবার কিংবা আপনজনদের কাছে প্রকাশ করলে তার মধ্যে যে জড়তা কাজ করে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। এসব ছোট ছোট কাজই একজন ব্যক্তিকে প্যানিক না করে বড় কিছু মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করে। একইসাথে একজন ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবেও গড়ে তোলে।
এই ফোবিয়ার আসলে নির্দিষ্ট বা সুষ্ঠু কোনো চিকিৎসা কিংবা ঔষধ আবিষ্কার হয়নি। এটা অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, যা সারানোর জন্য ধৈর্য এবং আশাবাদী থাকতে হবে। রোগী এবং রোগীর পরিবার উভয়ের জন্য এই কথা প্রযোজ্য। থেরাপিগুলোর মধ্যে ধ্যান করা, যোগ ব্যায়াম করা বা অন্য কোনো শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের সাথে এই বিষয়ে অবশ্যই কথা বলে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়া: স্কুলে যাওয়ার ভয়
অনেক শিশুই স্কুলে যেতে কিছুটা ভয় পায় কিংবা স্কুলে যাওয়ার প্রতি থাকে অনীহা। স্কুলের নাম বললেই হাজারো অজুহাতের বুলি শুনতে মা-বাবাকে। তবে ব্যাপারটির মধ্যে সাধারণত অস্বাভাবিকতার কোনো ছাপ দেখা যায় না। হঠাৎ করে মা-বাবা এবং পরিবার থেকে আলাদা হয়ে কয়েক ঘণ্টা অপরিচিতদের ভিড়ে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য মা-বাবাও এই বিষয়কে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন না। সময়ের সাথে প্রাকৃতিকভাবেই এই সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে, এমনটাই প্রত্যাশা তাদের। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমই হয়।
তবে কিছু কিছু শিশুর ক্ষেত্রে এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যে ভয়টা সময়ের সাথে আপনাআপনি কমে যাওয়ার কথা, তা দিন দিন বাড়তেই থাকে। দিন দিন এর প্রভাব একটি শিশুর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ ভাষায় একে ‘স্কুল অ্যাভয়ডেন্স’, ‘স্কুল রিফিউজাল’ বা ‘স্কুল ফোবিয়া' বলে।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়া নামে পরিচিত। দুর্লভ এই ফেবিয়ায় আক্রান্ত বিশ্বের ২ থেকে ৫ শতাংশ শিশু। শব্দটি গ্রিক ‘ডিডাস্কো’ এবং ‘ফোবোস’ থেকে এসেছে। ‘ডিডাস্কো’ অর্থ শেখানো এবং ‘ফোবোস’ বলতে ভয় বা ঘৃণাকে বোঝানো হয়। এই ফোবিয়াকে বোঝানোর জন্য ‘স্কোলিওনোফোবিয়া’ শব্দটিও ব্যবহার করা হয়, যার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘স্কিয়াস’ থেকে। এর অর্থ ‘জানা’। যেসকল বাচ্চা এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত, তাদের মধ্যে স্কুল পলায়নের প্রবণতা বা এ নিয়ে টালবাহানার অভ্যাস দেখা যায়। সাধারণত অনেক শিশুই স্কুলের নাম শুনলে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তবে ডিডাসক্যালেইনফোবিয়ায় আক্রান্ত কোনো শিশুর ক্ষেত্রে অবস্থাটি হয় বেশ বেগতিক। স্কুলের নাম শুনলেই তাদের প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে। মনোবিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের ফোবিয়া চার থেকে ছয় বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে মূলত দেখা যায়, যারা সাধারণত প্রি-স্কুলের শিক্ষার্থী। এই ফোবিয়া শনাক্ত করা কিছুটা কষ্টসাধ্য। কারণ এত ছোট বাচ্চারা নিজেদের অনুভূতি ভালোমতো প্রকাশ করতে পারে না। আর প্রকাশ করলেও ভয়টি স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক, তা বোঝাও কষ্টকর।
কারণগুলো কী?
এর চিকিৎসা করার পূর্বে অবশ্যই একটি শিশুর জীবন, বিশেষ করে তার স্কুল জীবন সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে, একদম ছোটখাট বিষয়গুলোও। যেমন- বাচ্চাটি স্কুলে বা স্কুল বাসে কোনো হেনস্তার শিকার হচ্ছে কি না, স্কুলে যাওয়ার পথে সে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার সম্মুখীন হয় কি না, তার শিক্ষক এবং সহপাঠীদের ব্যবহার সম্পর্কেও জানতে হবে। সব বিষয় জানার পরই কেবলমাত্র একটি শিশুর ক্ষেত্রে তার এই ফোবিয়ার আসল কারণ জানা সম্ভব। অবশ্যই সবার ক্ষেত্রে এর কারণ এক হয় না।
৪-৬ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় অনেকসময় কাজ করে। তাদের মনে হয় স্কুলে চলে গেলে পরে হয়তো আর মা-বাবার সাথে দেখাই হবে না। কোনো নেতিবাচক বা কষ্টদায়ক ঘটনা, যেমন- মা-বাবার মধ্যে মনোমালিন্য বা বিবাহবিচ্ছেদ, কোনো আপনজনের মৃত্যু ইত্যাদি এই ফোবিয়ার প্রভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটলে তা মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যা পরবর্তীতে ফোবিয়ার আকার ধারণ করে।
মাঝে মাঝে ১৩-১৫ বছর বয়সী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়া দেখা যায়। হঠাৎ করে স্কুলে পড়ার চাপ বাড়লে বা কঠিন কোনো বিষয়, যেমন- গণিত, বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে বুঝতে সমস্যা হলে তা মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।
এই বয়সী কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে। হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই তাদের বেশ ভুগতে হয়। এর মাঝে বাড়তি মানসিক চাপ আরো বেশি ক্ষতি করে।
তাছাড়া আরো কিছু ব্যাপার আছে। স্কুলের পরিবেশ নিরাপদ বা শিশুবান্ধব না হলে, যেমন- বুলিং, পড়া না পারলে কঠোর শাস্তি, স্কুলের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তির বিপজ্জনক আচরণ বা এরকম কোনো ঘটনা শিশুর মধ্যে ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়ার জন্ম দিতে পারে। আবার ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তন করলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভালো না মন্দ তা, নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে তাদের মনে। যে সন্দেহ কখন যে ভয়, আর ভয় থেকে পরবর্তীতে এই ফোবিয়ার জন্ম দেয়, তা সেই শিশু নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। কোনো ভীতিই আসলে একদিনে ফোবিয়ার আকার ধারণ করে না। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর এই সময়ের মধ্যে ভয়ের মূল বিষয়ের সাথে জড়িত ঘটনা ঘটলে তা দিন দিন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে।
লক্ষণসমূহ
ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশুর ক্ষেত্রে কিছু শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন-
১. স্কুলে যাওয়ার কথা বললেই অস্বাভাবিকভাবে কান্নাকাটি করা, কারো কারো ক্ষেত্রে প্যানিক অ্যাটাকও দেখা যেতে পারে। অনেক সময় একজন ফোবিক কিশোর-কিশোরী বা শিশু স্কুলে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সবসময় অসুস্থতার ভান করে কিংবা নিজেকে নিজেই ছোটখাট আঘাত করে, যার জের ধরে সে স্কুলে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারবে বলে মনে করে। আবার অনেকে রাতভর ইচ্ছা করে কান্নাকাটি করে, যাতে করে তাদের মা-বাবা বিরক্ত কিংবা ক্লান্ত হয়ে যায় এবং স্কুলে যাওয়া না লাগে। শুধু তা-ই নয়, এসব ফোবিক শিশু সবসময়ই নিজেদের মা-বাবাকে অনেক বেশি জ্বালায়। এর পেছনে তাদের সরল যুক্তি হলো, এতে করে তাদের অভিভাবকেরা স্কুলে যেতে জোর করবেন না। তবে ফলাফল যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর উল্টো হয়, তা-ও আর নতুন করে কিছু বলার নেই!
২. ফোবিক শিশুরা বেশিরভাগ সময়েই নেতিবাচক চিন্তা করে, বিশেষ করে মৃত্যু সম্পর্কিত। আপনজন এবং মা-বাবার খারাপ কিছু হতে পারে, এরকম চিন্তা মন ও মস্তিষ্ককে অবশ করে দেয়। ফলে তারা এক লহমার জন্যও তাদের ছেড়ে যেতে চায় না। আর এই কম বয়সে মা-বাবা তাদের বাচ্চাদের স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও এত বেশি সময়ের জন্য একা রাখে না। ফলস্বরূপ, ফোবিক শিশুর মনে স্কুলের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ক্ষোভ জন্মানোর বিষয়টা খুব অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য এই অবস্থায় শুধু স্কুলের প্রতি ভয় নয়, বরং বাসায় একা থাকার বা অন্ধকারে থাকার মতো ভয়, কিংবা ভূতের ভয়ও তার মধ্যে কাজ করে।
৩. কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে অবশ্য সবসময় একরকম ব্যবহার দেখা যায় না। তারাও শিশুদের মতো নিজেদের ফোবিয়ার কথা কাউকে বলে না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো তাদের কাছে বুঝিয়ে বলার ভাষা নেই আর কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা হলো, তাদের বলার কোনো ইচ্ছা নেই। সেজন্য তারা সবকিছু এড়িয়ে চলা শুরু করে। স্কুলে যাওয়া নিয়ে টালবাহানা এক্ষেত্রে আরো তীব্র হয়। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপও স্কুল ফোবিয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে।
৪. মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, শুকনো মুখ, ঘন ঘন ঘামা, ঊর্ধ্বশ্বাস, বমি বমি ভাব এবং প্যানিক অ্যাটাকের মতো লক্ষণগুলো ডিডাসক্যালেইনোফোবিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ কিছু শারীরিক পরিবর্তন।
প্রতিকার
কোনো ফোবিয়ারই আসলে স্থায়ী কোনো চিকিৎসা বা ঔষধ নেই। তবে যতটা সম্ভব একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।
যদি আপনি কোনো ফোবিক শিশুর অভিভাবক হন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে আপনার বাচ্চার প্রতি নমনীয় হতে হবে এবং খুব সতর্কতার সাথে ব্যাপারটা বুঝতে হবে।
একটি ইতিবাচক দিক হলো, বড়দের তুলনায় শিশু বা কমবয়সীদের মধ্যে নতুন কোনো চিন্তাধারা বা অভ্যাস গড়ে তোলা সহজতর। প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতে তারা তাদের ফোবিয়া ভুলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগও পেতে পারে। সেজন্য মা-বাবা এবং আপনজনদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। শিশুরা যেন মন খুলে তাদের সমস্যা বলতে পারে সেরকম বন্ধুসুলভ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔষধ গ্রহণেরও প্রয়োজন হয়। তবে অবশ্যই তা ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞদের কথা মতো সেবন করতে হবে। অবশ্য বিশেষজ্ঞের মতে, ঔষধ সেবনের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন এরকম ঔষধ খাওয়া ইতিবাচক নয়। মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আশেপাশের লোকজন সচেতন হলে একটি শিশুকে এই ফোবিয়ার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

ঘুমাতে ভয়! আপনি কি হিপনোফোবিয়ায় আক্রান্ত?
ঘুমাতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ বা প্রাণীকূল খুঁজে পাওয়া দুর্লভ বটে, কিন্তু এমন অনেক দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যারা কিনা ঘুমাতেই অত্যাধিক মাত্রায় ভয় পান। হ্যাঁ, এটা একধরনের রোগ। ঘুমের অনেক অসুখের মাঝে এই রোগটির নাম অন্তর্ভূক্ত। মেডিকেল টার্মে এই অসুখটি ‘হিপনোফোবিয়া’ নামেই পরিচিত। এছাড়াও এই রোগটিকে কোথাও কোথাও ক্লিনোফোবিয়া বা ওম্নিফোবিয়া নামেও নামকরণ করা হয়েছে।
নামকরণ বা উৎপত্তি
হিপনোফোবিয়া (Hypnophobia) নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ হাপনোস (Hupnos) এবং ফোবোস (Phobos) থেকে। গ্রিক ভাষায় হিপনোস শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘ঘুম’ এবং ফোবোস বা ফোবিয়া (Phobia) শব্দের অর্থ ‘ভয়’। গ্রিকদের ঘুমের দেবতাকে ডাকা হয় হিপনোস (Hypnos) নামে।
হিপনোফোবিয়া কেন হয়ে থাকে?
ঠিক কী কারণে অযাচিতভাবে মানুষ ঘুমাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয় তা বলা কঠিন। তবে ধারণা করা হয়, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি থেকেই মনের অগোচরে বাসা বাঁধে এই রোগ। অনেকের ক্ষেত্রে আবার সিনেমায় ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য (বিশেষত ভুতুড়ে সিনেমার দৃশ্য) মনে গেঁথে গেলে অথবা ঘনিষ্ঠজনের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো দুঃখজনক স্মৃতির সাক্ষী হয়ে থাকলে বা শৈশব (বিশেষত শৈশবের কোনো শারীরিক নিপীড়নের ঘটনা) অথবা জীবনের যেকোনো মুহূর্তে কোনো কারণে ভয় পাওয়ার নিদারূণ ঘটনা মনে গেঁথে থাকলে এসব ঘটনা আড়ালে-আবডালে ঘুমের সংশ্লিষ্টতায় ব্যাঘাত ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
অবচেতন মন তখন সব কিছুতেই তৈরি করে নেয় একধরনের আতংক বা ফোবিয়া, যা থেকে হিপনোফোবিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে আবার এই রোগের উৎপত্তিগত কারণ হিসেবে বংশানুক্রমিক বা জেনেটিক কারণকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকে।
হিপনোফোবিয়া আক্রান্তের লক্ষণ
হিপনোফোবিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণসমূহ চলুন জেনে নেয়া যাক-
১) অত্যাধিক মাত্রায় দুশ্চিন্তা এবং ভয়
২) শ্বাসের স্বল্পতা বা শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
৩) দ্রুত শ্বাস টানা
৪) হৃদযন্ত্রের অতিরিক্ত স্পন্দন
৫) মাত্রাতিরিক্ত ঘাম
৬) বিতৃষ্ণাবোধ
৭) মুখ শুকিয়ে যাওয়া
৮) মনোযোগের অভাব
৯) বাকযন্ত্রের আড়ষ্টতা
১০) মানসিক অস্থিরতা
১১) খিঁচুনি
১২) শরীর শক্তিশূন্য মনে হওয়া
১৩) সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ততা
১৪) অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা
১৫) মাথাব্যথা
১৬) সবকিছুতে বিরক্তি ভাব
১৭) ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা
১৮) ঘুমের মাঝে হাঁটা
১৯) অবচেতন মনে বিছানা ভিজিয়ে ফেলা
তবে ব্যক্তিবিশেষে রোগের লক্ষণ পাল্টে যেতে পারে। যেহেতু এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি, সে কারণে এই রোগের সঠিক চিকিৎসা সম্পর্কে কিছুটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। চলুন জেনে আসি কী কী উপায়ে এই রোগ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে।
হিপনোফোবিয়া আক্রান্ত হওয়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ
যেহেতু হিপনোফোবিয়া একটি মানসিক সমস্যা, তাই এক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, সময়মতো এই রোগ না সারালে সারাজীবন ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করাই ভবিতব্য বলে ধরে নেওয়া যায়। এই রোগের ক্ষতিকারক দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যে, এতে পারিবারিক অশান্তি ও সম্পর্কহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। সর্বোপরি, এক অসুখী জীবন, স্বাস্থ্যহানী, মনোসংযোগের অভাবও দেখা দেয়।
তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, হিপনোফোবিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে ৭০-৯০ ভাগ রোগী পুরোপুরিভাবেই সুস্থ হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে খুব দ্রুত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। চিকিৎসার বিলম্ব যতই ঘটবে, ততই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা বেড়ে যেতে থাকে। সাধারণত নবযৌবন বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নানা সমীক্ষায় প্রমাণ মেলে, মহিলাদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার পুরুষদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।
সমাজের যেকোনো স্তরের মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে রোগের উপসর্গের মাঝে পার্থক্য থাকতেই পারে। ভয় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সব সময় সিটিয়ে থাকে। বিশেষ করে কোনো কারণ ছাড়াই উদ্ভ্রান্তের মতো একের পর এক ভয় তাকে আক্রমণ করতে পারে এই ভেবেই মানুষ চিন্তামগ্ন দিনযাপন করে। এই ভয় পাওয়ার অনুভূতি মানুষের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই অবস্থান করে ও তার জীবনকে নষ্ট করে দেয়। অতীতে কোনো এক পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে থাকলে সেই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে স্বাভাবিকভাবেই কমবেশি সকলের গায়েই কাঁটা দিতেই পারে। কিন্তু এ ধরনের ভয় থেকে মনের অগোচরে তৈরি হয় একধরনের আতংক।
মহিলাদের হিপনোফোবিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি; Source: curemysleepapnea.com
যাদের মধ্যে আতঙ্ক বা ভয়-রোগ রয়েছে তারা যে ধরনের পরিস্থিতিতে ভয় পায় সেসব পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি প্রায়ই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। ফলে তাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এ থেকে নানা সামাজিক বিপত্তিও ঘটে যেতে পারে। শুধুমাত্র ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ততার কারণে অনেকে কর্মস্থলেও পিছিয়ে থাকে, ফলে ভালো কর্মীও হতে পারে না। মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও অবচেতন মনে অস্বাভাবিক ধরনের হয়ে থাকে। ভয়ের কারণে মানুষের ঘুমের সমস্যা তো এক প্রধান সমস্যা হয় বটেই, তাই রাতে জেগে থাকতে বাধ্য হতে হতে একসময় তৈরি হয় নানা মানসিক সমস্যা।
ভয়সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত অনেকেই তাদের রোগের উপসর্গ নিয়ে খুব চিন্তায় থাকেন। এমনকি ডাক্তার যদি আশ্বস্ত করে যে, এসব উপসর্গ মারাত্মক কিছু নয় তবুও তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ততায় দিন কাটান। অনেক ক্ষেত্রে অকারণে নিজেদের হার্টের রোগী, নিউরোলজিক্যাল রোগী বা কোনো মারাত্মক খারাপ অসুখের রোগী মনে করে ভয় পায় এবং প্রায়ই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটে যান। অনেকে আবার বারবার ডাক্তার পাল্টিয়ে যাচাই করার মানসিকতা দেখিয়ে থাকেন এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য কতগুলো অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বারবার করাতেই থাকেন। আসলে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই, তবে এতে করে রোগী সাময়িকভাবে মানসিক সান্ত্বনা খুঁজে পেতেও পারেন।
ভয় বা আতংক থেকে মানুষ তার বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বা নিজের প্রতি আস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ভয়ের উপসর্গগুলো সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উপসর্গগুলো আস্তে আস্তে বিলীন হওয়ার জন্য ঘণ্টাখানেক বা বছরের পর বছর সময়ও লাগতে পারে। যারা ভয়ের কারণে ঘুমাতে পারেন না তারা সবসময় তাদের ভেতরের অসহ্য অস্থিরতার কথা প্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় তারা পাগলাটে ধরনের আচরণ করে থাকে।
প্রচন্ড মানসিক চাপের দরূণ ভয় সৃষ্টি হওয়া বা কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা প্রভৃতি কারণেও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া অতিরিক্ত চা-কফি খাওয়া, কোকেন বা অন্য কোনো উত্তেজক ওষুধ অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলেও ভয়ের সৃষ্টি হতে পারে। ভয় মানুষকে হতভম্ব করে দেয়।
এর ক্ষতিকর প্রভাব কী বা কতটুকু তা আগে থেকে বলা কঠিন। যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়নি তারা অনেক সময় মনে করে যে, ভয় হচ্ছে কোনো বিষয়ে নার্ভাস বা উদ্বিগ্ন হওয়া, যা কম-বেশি সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অনেক সময় কেউ ভয় পেলে তার মনের ভেতরে যেসব অস্থিরতা দেখা দেয় বাইরে থেকে তা বোঝা কঠিন।
সাধারণত যারা খুব অল্প সময় ভয়ে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত তাদের জীবনে এর মারাত্মক কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যারা বারবার ভয়ে আক্রান্ত হয় এবং এ থেকে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না তাদের জীবনে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। পরিবারের কোনো এক সদস্যও যদি হিপনোফোবিয়া আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে পরিবারের অন্যদের জন্যও এটি দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রোগীর চিকিৎসার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের সদয় দৃষ্টি দেওয়া খুব প্রয়োজন এবং সময়মতো রোগীকে একবার অন্তত মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।
তাছাড়া অনেক সময় সাময়িক চিকিৎসা এবং থেরাপিস্টের পরামর্শেও উপকার পাওয়া যায় বৈকি, তবে এক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক রোগীকে তার নিকটজনের সময় দেয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভয়রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো রোগী যেসব অবস্থা বা পরিস্থিতিকে ভয় পায় তার সঠিক অনুসন্ধান করে সেসব পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে যাওয়া এবং তার ভুল ভাঙ্গানোর চেষ্টা করা। পরিবারের কাছের মানুষেরাই এ কাজটি করতে পারে। একমাত্র রোগীর কাছের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে এমন ভয়রোগে আক্রান্ত রোগীকে পুরোপুরিভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে।
চিকিৎসা পদ্ধতি
হিপনোফোবিয়া থেকে মুক্তি পেতে কাউন্সেলিং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সমাধান। তবে সমস্যা হলো এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ হওয়াতে রোগীকে দীর্ঘদিন যাবত আতঙ্কে সময় কাটাতে হওয়ার ভোগান্তিতে ভুগতে হয়। বেশিরভাগ থেরাপি বলতে গেলে সময়সাপেক্ষ। তাই বলে চিকিৎসা পদ্ধতির অবদান কিন্তু থেমে নেই। পদ্ধতিগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-
১) কগনিটিভ থেরাপি (Cognitive Therapy or CT)
২) কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি (Cognitive Behavior Therapy)
৩) হ্যাবিট স্ট্রাটিজিস টু রিল্যাক্স (Habit Strategies to Relax)
৪) ইন ভিভো এক্সপোজার (In Vivo Exposure)
৫) রেস্পন্স প্রিভেনশান (Response Prevention)
৬) হিপনোথেরাপি
৭) গ্রুপ থেরাপি
৮) সাইকো থেরাপি
৯) এনার্জি সাইকোলজি
১০) পথ্য (Medication) এবং
১১) মেডিটেশান বা ধ্যান
ক্যাটসারিডাফোবিয়া: তেলাপোকা ভীতির খুঁটিনাটি
তেলাপোকা ভয় পাওয়া খুব সাধারণ একটি বিষয়। পৃথিবীতে যত প্রজাতির তেলাপোকা রয়েছে, তার মাত্র এক শতাংশই মানুষের সঙ্গে বসবাস করে। এরা সরাসরি কোনো রোগ বিস্তার করে না বা মানুষের খুব বড় ধরনের কোনো ক্ষতিও করে না। তা সত্ত্বেও মানুষ সচরাচর যেসব ফোবিয়া বা ভীতিতে ভুগে থাকে, তেলাপোকা-ভীতি বা ক্যাটসারিডাফোবিয়া তার মধ্যে অন্যতম। পূর্বে এটিকে এনটোমোফোবিয়া বা পোকামাকড়-ভীতির মধ্যেই ধরা হতো। পরবর্তীতে এটিকে আলাদা করে ‘ক্যাটসারিডাফোবিয়া’ নাম দেওয়া হয়।
ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইওমিং এর ইকোলজি বিষয়ের অধ্যাপক জেফ্রি লকউড তেলাপোকা-ভীতি প্রসঙ্গে বলেন, “ভয় ও বিরক্তি মানুষের দুটি সার্বজনীন নেতিবাচক আবেগ। এর একটি তাৎক্ষণিক বিপদ নির্দেশ করে আর অপরটি রোগবালাই বা দূষণের সম্ভাবনার সংকেত দেয়।” তার মতে, তেলাপোকা মানুষের মনে বিরক্তি ও ভয়- দুটি অনুভূতিকেই সক্রিয় করে তোলে। এর শরীরের তৈলাক্ত, চটচটে ভাব, রাতের আঁধারে গায়ের ওপর হেঁটে বেড়ানো কিংবা ভুলবশত পায়ের নিচে চাপা পড়ার ফলে বেরিয়ে আসা ইউরিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধ স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি জাগায়। অপরদিকে হরর ছবির ভূতুড়ে কোনো চরিত্রের মতো দ্রুততার সঙ্গে উড়ে বেড়ানো, মানুষেরই ঘরে গোপনে বাস করে হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেওয়া কিংবা তার অদ্ভুতুড়ে পা ও অ্যান্টেনার গঠন মানুষের মনে রহস্য ও ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে। তেলাপোকার প্রতি মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণার এটিই হয়তো মূল কারণ। তবে এটি কেবল স্বাভাবিক একটি প্রতিক্রিয়া, কোনো ফোবিয়া নয়।
তেলাপোকা-ভীতি বা ‘ক্যাটসারিডাফোবিয়া’ শব্দটি সেক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে, যখন একজন ব্যক্তি তেলাপোকার প্রতি দীর্ঘদিন ধরে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ধরনের ভয় পোষণ করে, এবং এই ভয়ের ফলে তার মারাত্মক শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারেন যে, তেলাপোকা মোটামুটি নিরীহ ধরণের প্রাণী এবং এটি মানুষের জন্য বড় কোনো হুমকি বয়ে নিয়ে আসে না। এমনকি তারা তাদের এই ভীতি নিয়ে বিব্রতও বোধ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের মনে উদ্ভূত ভয় এবং উদ্বেগ এড়িয়ে যেতে পারেন না।
ক্যাটসারিডাফোবিয়ার কারণ
বিবর্তনগত কারণ: রাতে বা অন্ধকার পরিবেশে এটি বেরিয়ে এসে শরীরের ওপর হেঁটে বেড়ালে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি হয়, যার ফলে আমরা ভয় বা বিরক্তি অনুভব করি। এই অনুভূতিটি বিবর্তনগতভাবে আমাদের মধ্যে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন গুহায় বাস করতেন, তখন তাদেরকে সবসময় এ জাতীয় পোকামাকড়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হতো। সেই থেকেই মানুষের মনে কীটপতঙ্গের প্রতি একধরনের আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে।
শৈশবের নেতিবাচক স্মৃতি: সাধারণত উষ্ণ ও
তেলাপোকা ভয় পাওয়া খুব সাধারণ একটি বিষয়। পৃথিবীতে যত প্রজাতির তেলাপোকা রয়েছে, তার মাত্র এক শতাংশই মানুষের সঙ্গে বসবাস করে। এরা সরাসরি কোনো রোগ বিস্তার করে না বা মানুষের খুব বড় ধরনের কোনো ক্ষতিও করে না। তা সত্ত্বেও মানুষ সচরাচর যেসব ফোবিয়া বা ভীতিতে ভুগে থাকে, তেলাপোকা-ভীতি বা ক্যাটসারিডাফোবিয়া তার মধ্যে অন্যতম। পূর্বে এটিকে এনটোমোফোবিয়া বা পোকামাকড়-ভীতির মধ্যেই ধরা হতো। পরবর্তীতে এটিকে আলাদা করে ‘ক্যাটসারিডাফোবিয়া’ নাম দেওয়া হয়।
ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইওমিং এর ইকোলজি বিষয়ের অধ্যাপক জেফ্রি লকউড তেলাপোকা-ভীতি প্রসঙ্গে বলেন, “ভয় ও বিরক্তি মানুষের দুটি সার্বজনীন নেতিবাচক আবেগ। এর একটি তাৎক্ষণিক বিপদ নির্দেশ করে আর অপরটি রোগবালাই বা দূষণের সম্ভাবনার সংকেত দেয়।” তার মতে, তেলাপোকা মানুষের মনে বিরক্তি ও ভয়- দুটি অনুভূতিকেই সক্রিয় করে তোলে। এর শরীরের তৈলাক্ত, চটচটে ভাব, রাতের আঁধারে গায়ের ওপর হেঁটে বেড়ানো কিংবা ভুলবশত পায়ের নিচে চাপা পড়ার ফলে বেরিয়ে আসা ইউরিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধ স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি জাগায়। অপরদিকে হরর ছবির ভূতুড়ে কোনো চরিত্রের মতো দ্রুততার সঙ্গে উড়ে বেড়ানো, মানুষেরই ঘরে গোপনে বাস করে হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেওয়া কিংবা তার অদ্ভুতুড়ে পা ও অ্যান্টেনার গঠন মানুষের মনে রহস্য ও ভয়ের অনুভূতি তৈরি করে। তেলাপোকার প্রতি মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণার এটিই হয়তো মূল কারণ। তবে এটি কেবল স্বাভাবিক একটি প্রতিক্রিয়া, কোনো ফোবিয়া নয়।
তেলাপোকা-ভীতি বা ‘ক্যাটসারিডাফোবিয়া’ শব্দটি সেক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে, যখন একজন ব্যক্তি তেলাপোকার প্রতি দীর্ঘদিন ধরে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ধরনের ভয় পোষণ করে, এবং এই ভয়ের ফলে তার মারাত্মক শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারেন যে, তেলাপোকা মোটামুটি নিরীহ ধরণের প্রাণী এবং এটি মানুষের জন্য বড় কোনো হুমকি বয়ে নিয়ে আসে না। এমনকি তারা তাদের এই ভীতি নিয়ে বিব্রতও বোধ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের মনে উদ্ভূত ভয় এবং উদ্বেগ এড়িয়ে যেতে পারেন না।
ক্যাটসারিডাফোবিয়ার কারণ
বিবর্তনগত কারণ: রাতে বা অন্ধকার পরিবেশে এটি বেরিয়ে এসে শরীরের ওপর হেঁটে বেড়ালে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি হয়, যার ফলে আমরা ভয় বা বিরক্তি অনুভব করি। এই অনুভূতিটি বিবর্তনগতভাবে আমাদের মধ্যে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন গুহায় বাস করতেন, তখন তাদেরকে সবসময় এ জাতীয় পোকামাকড়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হতো। সেই থেকেই মানুষের মনে কীটপতঙ্গের প্রতি একধরনের আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে।
শৈশবের নেতিবাচক স্মৃতি: সাধারণত উষ্ণ ও অন্ধকার জায়গায় তেলাপোকা লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। ছোটবেলায় যাদেরকে এমন অন্ধকার ঘর বা আলমারির ভেতর বন্দী করে রেখে শাস্তি দেওয়া হয় যেখানে তেলাপোকার বসবাস রয়েছে, তাদের মনে বড় হওয়ার পরেও সেটির বিরূপ প্রভাব থেকে যায় এবং সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তাদের মনে তেলাপোকা-ভীতি তৈরি হতে পারে।
আশেপাশের বড়দেরকে তেলাপোকা ভয় পেতে দেখলে অনেক সময় ছোটরাও তেলাপোকাকে ভয় পেতে শুরু করে।
তেলাপোকা নিজে সরাসরি কোনো রোগের জন্যে দায়ী না হলেও এটি বিভিন্ন রোগের বিস্তারে সাহায্য করতে পারে। এই ক্ষতিকারক প্রভাবের কারণেও মানুষের মনে তেলাপোকা নিয়ে শংকা জাগতে পারে।
তেলাপোকার পচা-বাসী খাবার খাওয়ার নোংরা স্বভাব কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার অকল্পনীয় ক্ষমতাও মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করতে পারে।
তেলাপোকা কীভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে?
খাদ্যদ্রব্য ঢেকে না রাখলে তেলাপোকা তাতে আক্রমণ করে। খাওয়ার সময় এরা মুখ থেকে লালা এবং হজমে সহায়ক তরল পদার্থ উদগিরণ করে। ফলে তেলাপোকার অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুসমূহ খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। Pseudomonas aeruginosa নামক ব্যাকটেরিয়া তেলাপোকার অন্ত্রে ব্যাপকভাবে বংশবিস্তার করতে সক্ষম। এই ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে মূত্রনালীর সংক্রমণ, হজমে গোলযোগ এবং রক্তদূষণ ঘটাতে পারে। এছাড়া খাদ্যে বিষক্রিয়া ও টাইফয়েড রোগের জন্যে দায়ী Salmonella ব্যাকটেরিয়াও তেলাপোকার মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
তেলাপোকা সর্বভুক প্রাণী। গাছ ও প্রাণীর মৃতদেহ, বিষ্ঠা, সাবান, আঠা, কাগজ, চামড়া, চুল ইত্যাদি এমন কিছু হয়তো নেই, যা তারা খায় না। ফলে এরা শুধু খাবারে মুখ দিলেই নয়, খাবারের ওপর মল ত্যাগ করলেও খাবার দূষিত হতে পারে। সাধারণভাবে তেলাপোকার কামড়ানোর প্রবণতা কম, তবে হাত-পায়ের আঙুল বা নরম চামড়ায় এটি কামড় দিতে পারে। এছাড়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তির নাক বা কানের ফুটো দিয়ে ছোট আকৃতির তেলাপোকা ঢুকে যেতে পারে। তেলাপোকার লালা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন রয়েছে, যা মানুষের শরীরে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং যার ফলে হাঁপানি রোগীদের হাঁপানির আক্রমণের প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।
কখন বুঝবেন, ক্যাটসারিডাফোবিয়ায় ভুগছেন?
এই ফোবিয়ার লক্ষণগুলো একেকজনের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে। কারো হয়তো সামনাসামনি তেলাপোকা দেখলে ভয় হয়, আবার কেউ হয়তো তেলাপোকার ছবিও দেখলে ভয় পান। খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে ক্যাটসারিডাফোবিয়ার লক্ষণ হচ্ছে, তেলাপোকাকে প্রচণ্ড ভয় পাওয়া এবং তেলাপোকা আছে, এমন কোনো পরিবেশে থাকতে উদ্বেগ বা অস্বস্তি বোধ করা।
এছাড়া যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তা হলো-
তেলাপোকা দেখলে ভয়ে স্থির হয়ে যাওয়া, নড়াচড়া করতে না পারা।
চিৎকার-চেঁচামেচি বা কান্না করা।
অনেক সময় ‘অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারে’র অংশ হিসেবে ক্যাটসারিডাফোবিয়া দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ব্যক্তির মধ্যে তেলাপোকা দূর করার জন্যে ঘরের ভেতর বারবার কীটনাশক স্প্রে করা, কার্পেট ঝাড়া ও মোছা, রান্নাঘর ও স্নানঘর পরিস্কার করার অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেয়।
অতিরিক্ত ভয় বা উদ্বেগের কারণে প্যানিক অ্যাটাক হওয়া, যার লক্ষণসমূহ হচ্ছে- মাথা ঝিমঝিম করা, হাঁটু অবশ বোধ হওয়া, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, দুর্বল বোধ করা, বুকে ব্যথা হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
কীভাবে তেলাপোকা-ভীতি কাটিয়ে ওঠা যায়?
যেকোনো ভীতি দূর করতে হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই সেই ভয়ের মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস অর্জন করতে হবে। তিনি নিজে ভয় কাটিয়ে উঠতে ইচ্ছুক হলে একজন থেরাপিস্ট বা বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন। তেলাপোকা ভীতি সারাতে মনোচিকিৎসা অনেকাংশেই সফল হয়। চিকিৎসার অংশ হিসেবে বিভিন্ন থেরাপির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে সকল রকমের চিকিৎসা কেবলমাত্র চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই করতে হবে।
সিস্টেমিক ডিসেনসিটাইজেশন: এই থেরাপির ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার ভয়ের সম্মুখীন করা হয়। তেলাপোকার ছবি দেখানো থেকে শুরু করে দূর থেকে জীবন্ত তেলাপোকা দেখা, মৃত তেলাপোকা স্পর্শ করা, তেলাপোকার সাথে একা একটি ঘরে থাকা, জীবন্ত তেলাপোকা স্পর্শ করা- এসবের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তেলাপোকার সঙ্গে অভ্যস্ত করে তোলা হয়।
কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি: এই থেরাপি ভয়ের সেই নির্দিষ্ট বস্তুটির (অর্থাৎ তেলাপোকা) ব্যাপারে আক্রান্ত ব্যক্তির নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।
নিউরো-লিংগুইস্টিক প্রোগ্রামিং: এ পদ্ধতিতে প্রথমে ভয়ের প্রকৃত কারণ সনাক্ত করা হয় এবং পরে সাইকোথেরাপি, আত্মউন্নয়ন, শিথিলায়ন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়।
ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি থেরাপি: এই পদ্ধতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ভার্চুয়াল পর্দায় তার ভয়ের সম্মুখীন করে ভয় কাটানোর চেষ্টা করা হয়।
তেলাপোকার উপস্থিতিতে যাদের তীব্র ভয় এবং প্যানিক অ্যাটাক দেখা দেয়, তাদের চিকিৎসায় ঔষধও প্রয়োগ করতে হতে পারে।
কারো তেলাপোকা-ভীতি থাকুক বা না থাকুক, বাড়িতে তেলাপোকা থাকা মোটেও ভাল কোনো ব্যাপার নয়। তাই ঘরে তেলাপোকার আনাগোনা বন্ধ করতে নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করা যেতে পারে–
ঘর সবসময় পরিস্কার রাখুন। তেলাপোকারা দল বেঁধে ঘরের অন্ধকার, স্যাঁতসেতে ও উষ্ণ কোণে লুকিয়ে থাকে। রান্নাঘর, শৌচাগার এবং খাওয়ার ঘরেই এদের বেশি দেখা যায়। এরা বিশেষত উচ্ছিষ্ট, তৈলাক্ত খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই চুলার আশপাশের অংশ, খাওয়ার টেবিল ও ঘরের মেঝে সবসময় মুছে পরিস্কার রাখুন। রাতে ঘুমানোর আগে সিংকে জমা হওয়া নোংরা তৈজসপত্র ধুয়ে ফেলুন। ময়লার ঝুড়ি সবসময় ঢেকে রাখুন এবং প্রতি রাতে তা খালি করে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত একবার রেফ্রিজারেটর পরিষ্কার করুন।
খাবারের দূষণ এড়াতে হলে খোলা অবস্থায় খাবার ফেলে রাখবেন না।
দেয়ালে তৈরি হওয়া ছিদ্র বা ফাটলের মধ্য দিয়ে সহজেই ঘরে তেলাপোকা প্রবেশ করতে পারে। তাই যেকোনো ছিদ্র বা চিড় চোখে পড়ামাত্রই তা বন্ধ করে দিন।
পুরনো খবরের কাগজ, বই ও ম্যাগাজিনের স্তূপ খোলামেলা জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
ভেজা, স্যাঁতসেতে পরিবেশ তেলাপোকার বেশ পছন্দ। সুতরাং তেলাপোকা থেকে রেহাই পেতে বাড়ির পানি প্রবাহের পথে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সারিয়ে নিন। সিংকে পানি জমিয়ে রাখবেন না এবং ঘরের ভেতর টবে গাছ থাকলে তাতে অতিরিক্ত পানি দেবেন না।
গরম পরিবেশে তেলাপোকারা বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাই ঘরবাড়ি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন।
বাজারে তেলাপোকা নিধনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের ভেতর বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে না চাইলে সরাসরি তেলাপোকার গায়ে সাবান-পানির মিশ্রণ তৈরি করে তা স্প্রে করলেও পোকা মারা যাবে। এছাড়া তিন ভাগ বোরিক অ্যাসিড ও এক ভাগ গুঁড়ো চিনির মিশ্রণ তৈরি করে তেলাপোকার চলাচলের জায়গায় টোপ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

মোবাইলে আসক্তির নতুন নাম নোমোফোবিয়া
আর দশটা মানুষের মত বর্তমান সময়ে আপনার হাতেও একটি মোবাইল ফোন থাকাটা স্বাভাবিক। তবে আপনার মোবাইল ফোনের সাথে যদি নিজেকে মানসিকভাবে জড়িয়ে ফেলেন তাহলে ব্যাপারটা আর স্বাভাবিক থাকে না। মোবাইল ফোনের সাথে এর ব্যবহারকারীর এই যে অতিমাত্রায় মানসিক সংযোগ, মানসিক চিকিৎসকেরা এর নাম দিয়েছেন ‘নোমোফোবিয়া’।
নোমোফোবিয়া শব্দটি এসেছে নো (NO), মো (MOBILE) এবং ফোবিয়া (PHOBIA) থেকে। যেটাকে একসাথে করলে হয় মোবাইল ফোন নেই- এমন ফোবিয়া। বর্তমানে পৃথিবীতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। সাধারণ মোবাইল ফোনের পাশাপাশি বেড়ে চলেছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণানুসারে, বর্তমানে শুধু আমেরিকার মোট জনসংখ্যারই ৯০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, যাদের ৫০ শতাংশ হল স্মার্টফোন ব্যবহারকারী। এছাড়া পৃথিবীতে প্রায় ৬.৮ বিলিয়ন মোবাইল ফোন গ্রাহক রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক তো খুব সাধারণ একটি অ্যাপ। আর দশটা অ্যাপের মত। কিন্তু বর্তমানে ফেসবুক ছাড়া আমাদের একটা মিনিটও চলে না। কোনো অ্যাপ নয়, এটি যেন আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। ঠিক একইভাবে, মোবাইল ছাড়াও বর্তমানে মানুষ নিজের জীবনকে ভাবতে পারে না। মোবাইল কাছে নেই বা মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছে- এটাও অনেকের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।
মোবাইল ফোন অত্যন্ত দরকারি একটি জিনিস। সেটি নষ্ট হলে বা না থাকলে মানসিকভাবে একটু চিন্তায় পড়তেই পারেন আপনি। কিন্তু তাই বলে সেটা মাত্রা ছাড়াবে এমন তো নয়। তবে কারো ক্ষেত্রে যদি ব্যাপারটি গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে, সেটাকে আর স্বাভাবিক বলা যায় না। তখন এই মানসিক সমস্যাকে নোমোফোবিয়া বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ফোবিয়া বা ভীতি বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ফোন না থাকার ভীতি বা নোমোফোবিয়ায় এমন অনেক কিছু ঘটে যা খুব বেশি বড় আর চোখে পড়ার মত না হলেও, একটু একটু করে মানসিক নানাবিধ সমস্যা তৈরি করে।
নোমোফোবিয়ার উপসর্গ
নোমোফোবিয়ার উপসর্গগুলো খুব সাধারণ। বিশেষ করে, বর্তমানে আমাদের মধ্যে ব্যাপারগুলো এত সহজভাবে মিশে গিয়েছে যে, এগুলোকে আর আলাদা করে কিছু মনে হয় না। বরং অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। এই যেমন ধরুন, আপনি খাচ্ছেন বা রাস্তায় হাঁটছেন। হঠাৎ আপনার মনে হল পকেটের ফোনটা হয়তো বেজে উঠেছে। কিন্তু ফোন হাতে নিয়ে দেখলেন, না! কেউই ফোন করেনি আপনাকে। এই যে ছোট্ট আর অতি সামান্য ঘটনাটি ঘটে গেল আপনার সাথে এটিও কিন্তু নোমোফোবিয়ারই অংশ!
এছাড়াও নোমোফোবিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশ কিছু উপসর্গ দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-
১। মোবাইলের কাছ থেকে দূরে থাকলে চিন্তিত হয়ে পড়া, অস্থিরতায় ভোগা।
২। কোনো কাজে বা কারো কথায় মন না দিতে পারা। একটু পরপর ফোন হাতে নিয়ে দেখা কেউ কল দিল কিনা বা বার্তা পাঠালো কিনা।
৩। সেলফোন ভাইব্রেশন সিনড্রোম বা মোবাইলের কম্পন বারবার অনুভব করা।
৪। ফোন না থাকলে নিজেকে একা মনে হওয়া, হতাশ হয়ে পড়া।
ইউনিভার্সিটি অব কানেক্টিকাট স্কুল অব মেডিসিনের মনোরোগবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক ডক্টর ডেভিড গ্রিনফিল্ডের মতে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের মস্তিষ্কে ডোপামিনের স্বাভাবিক পরিমাণ কমে যায়। ডোপামিন মানুষকে নতুন কোনো কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করে। মোবাইল যেহেতু সেটাকে কমিয়ে দেয়, ফলে অন্য কোনো কাজে তারা আর উৎসাহ খুঁজে পায় না। মোবাইলের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকবার একেকটি নোটিফিকেশন বা বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্কে একটু করে ডোপামিনের সরবরাহ ব্যাহত হয়। মস্তিষ্ক দ্বিধায় পড়ে যায় এটা ভাবতে গিয়ে যে, কখন নতুন কোনো বার্তা বা নোটিফিকেশন আসবে ফোনে। আমাদের পুরো চিন্তাভাবনা আর মস্তিষ্কের সমস্ত কাজেই প্রভাব পড়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, আমরা একটা সময় এই মানসিক অবস্থাটির সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাই। এই যে অস্বস্তিতে থাকা, মোবাইলের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়া, ডোপামিনের একটু কম সরবরাহ- এতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, এই ব্যাপারগুলো না থাকলে নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না আমাদের মস্তিষ্ক; নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়, নোমোফোবিয়া জন্ম নেয়।
২০১৩ সালে করা একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্তত ৯ শতাংশ মানুষ প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর নিজেদের মোবাইল দেখেন। বাকিরাও যে খুব একটা পিছিয়ে আছেন এদিক দিয়ে তা কিন্তু নয়। এছাড়াও এই পরীক্ষাটিতে আরো জানা যায় যে, বাড়িতে ফোন ফেলে আসা মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৬৩ শতাংশ মানুষ ঐ দিনের পুরোটা সময় হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকেন। ইউগভ এবং হাফিংটন পোস্টের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, অধিকাংশ মানুষই রাতে ঘুমানোর সময় সাথে মোবাইল ফোন না থাকলে অস্বস্তি বোধ করেন এবং ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৬৪ শতাংশ মানুষ মোবাইল ব্যবহার করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েন।
নোমোফোবিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নারী নয়, পুরুষরাই নোমোফোবিয়ার বেশি ভুক্তভোগী হয়ে থাকে। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করার ফলে নোমোফোবিয়া সৃষ্টি হয় এবং সেটি কেবল মানসিক নয়, আমাদেরকে শারীরিকভাবেও প্রভাবিত করে। তাই আপনিও যদি নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত হন, কিংবা আসক্ত যদি হয় আপনার সন্তান বা আশেপাশের মানুষ, তাহলে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন।
১। দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় মোবাইলকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখুন। তার মানে এই নয় যে, সেই সময় আপনাকে ফোন করলে কেউ পাবে না। তবে মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রেখে, সেটাকে একটু দূরে রেখে দিন যাতে করে কেউ আপনাকে ফোন করলে খুঁজে পায়। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। অন্যথায়, চোখের সামনে ফোন থাকলে বা ফেসবুক এবং অন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বারবার নোটিফিকেশন আসলে আপনি মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন।
২। ঘুমানোর সময় মোবাইল দূরে রাখুন। সম্ভব হলে বন্ধ কিংবা সাইলেন্ট করে রাখুন। কিছুদিন এই পদ্ধতি মেনে চললে আপনার চারপাশের মানুষ ব্যাপারটি বুঝতে পারবে এবং রাতের নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর আপনাকে আর কল করবে না। ঘুমের ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট সময় মেনে চলুন। অনেকেই রাতে ঘুম না আসার কারণে মোবাইল ব্যবহার করেন এবং খানিক পর ঘুম আসলেও আর মোবাইলের কারণে ঘুমাতে পারেন না। তাই ঠিক সময়ে প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়ুন। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হবে।
৩। কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগে? কোনো কাজ করতে গেলে সময় কেটে যায়? এই মানুষ এবং কাজগুলোকে চিহ্নিত করুন এবং এই ব্যাপারগুলো নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। বিনা কারণে ফোনের দিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার সমস্যা একটু হলেও কমে যাবে।
৪। মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করুন। চেষ্টা করুন ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপে এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের। বর্তমানে আমাদের মোবাইলের আসক্তি এবং নোমোফোবিয়া নামক মানসিক সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তাই এর ব্যবহার কমিয়ে ফেলুন। এতে করে সমস্যা একটু হলেও দূর হবে।

মনোফোবিয়া: একা হয়ে যাবার ভয়
কেস স্টাডি ১
দিনা (ছদ্মনাম) তার বিবাহিত জীবনে অসুখী একজন মহিলা। তিনি বিয়ের প্রায় দশ বছরের মাথায় বুঝতে পারেন তার স্বামী আরেকজনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছেন। দিনার দুটি ফুটফুটে সন্তান আছে। তিনি যথেষ্ট সুন্দরী একজন মহিলা এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। তিনি চাইলেই আলাদা হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তবুও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার করে যাচ্ছেন। কারণ তিনি একা থাকতে ভয় পান। এই সংসারে অন্তত রাতে শোবার ঘরে কেউ থাকে। কিন্তু সংসার ছেড়ে চলে গেলে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বেন। তার ধারণা, তিনি একা থাকলে মারা যাবেন অথবা কেউ তাকে মেরে ফেলবে। তার স্বামী মানুষটা যেমনই হোক, তিনি আশেপাশে থাকলেই দিনা নিরাপদ!
কেস স্টাডি ২
রুপক (ছদ্মনাম) বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বয়স বিশের কাছাকাছি। পড়াশোনায় খুব ভালো। কিন্তু ছেলেটি এখনও তার মাকে ছাড়া কোথাও চলাফেরা করতে পারে না। রাতে মাকে পাশে নিয়ে ঘুমায়, সকালে মা তাকে ভার্সিটিতে রেখে আসে, ফেরার পথে মা তাকে নিয়ে আসে, খাবার সময় মায়ের সাথেই খায়, এমনকি গোসলের সময়ও মাকে দরজার বাইরে থাকতে হয়। রুপকের বাবা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। মা নীরবে চোখ মোছেন।
উপরে যে দুটি ঘটনা বলা হলো এখানে দিনা এবং রুপক একটি ফোবিয়ায় আক্রান্ত। এই ফোবিয়ার নাম মনোফোবিয়া।
মনোফোবিয়া হলো একধরনের মানসিক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ সবসময় একা হয়ে যাবার ভয়ে আতংকিত থাকে। শুধু মানুষই না, পশুরাও এই রোগে ভোগে। মনোফোবিয়া কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ কোনো ব্যাপার নয়। সত্যিকার অর্থে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গী এমন হয় যে তার কাছের মানুষকে খুব বেশি ভালবাসছে বলেই তাকে চোখের আড়াল করতে চাইছে না। এমন ইতিবাচক একটি লক্ষণ থাকায় কেউই এটাকে রোগ মনে করেন না। কিন্তু ভুক্তভোগী বিভিন্ন সময় দুশ্চিন্তায় বিভোর থাকেন।
এই রোগকে অটোফোবিয়া বা ইসোলাফোবিয়াও বলা হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সবসময় তার মধ্যে উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা এবং একা হয়ে যাবার ভয় পেতে দেখা যায়। ফলে তার ঘুম, খাওয়া, এমনকি একা বাথরুমে যেতেও সমস্যা হয়। মনোফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষ স্বাভাবিক কোনো কাজ করতে পারে না। মাঝে মাঝে তার এই অতিরিক্ত সাথে সাথে থাকার প্রবণতা থেকে কাছের মানুষের সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে, যা তার জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর।
মনোফোবিয়ার লক্ষণসমূহ
অস্থির লাগা, মাথা ঘোরা, হাত পা অবশ হয়ে আসা
কেউ গলা চেপে ধরছে এমন বোধ হওয়া
ঘন ঘন হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া
প্রচুর ঘাম হওয়া
বুকে ব্যথা
বমি বমি ভাব হওয়া
হঠাৎ করে অসাড় হয়ে যাওয়া
আরও কিছু লক্ষণ
বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা
মারা যাবার দুশ্চিন্তা হওয়া
কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেলার ভয়
হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লাগা, আবার গরম লাগা
জ্ঞান হারিয়ে ফেলা
মনোফোবিয়ার কারণ
এই রোগের উৎপত্তি বা কারণ নির্দিষ্ট করে বলা একটু কঠিন। কারো হয়তবা ছোটবেলায় কোনো বড় দুর্ঘটনা থেকে হতে পারে, কারো চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে, কারো বা খুব কাছের মানুষের মৃত্যু থেকেও এমনটা হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে পুষে রাখা দুশ্চিন্তা, সম্পর্কে অবনতি, বাসায় অসঙ্গতিমূলক পরিবেশ ইত্যাদিও মনোফোবিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
এটাও বলা যায় যে, যারা খুব বেশি উদ্বিগ্নতার মাঝে থাকেন, একটা সময় তাদের ভিতর মনোফোবিয়া তৈরি হয়। যে সকল বাচ্চা নিজেদের বাবা-মায়ের কাছে কম সময় পায় বা বাড়িতে গৃহকর্মীদের নিকট বড় হয়, তাদের মাঝেও বিভিন্ন রকম ফোবিয়া দেখা দেয়। যারা মনোফোবিয়ায় ভোগেন তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে। এরা সাধারণত নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষটার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে থাকে।
মনোফোবিয়ার চিকিৎসা
মনোফোবিয়ার চিকিৎসা আসলে মানসিকভাবে হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধ্যান, কোনো সেমিনারে অংশগ্রহণ করা বা ব্যক্তিগতভাবে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে এই রোগের প্রভাব অনেকটা কমিয়ে আনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ ভালো করা সম্ভব। হিপনোথেরাপির মাধ্যমেও এর চিকিৎসা সম্ভব। শুধুমাত্র ওষুধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা হয় না। তবে স্নায়ু ঠাণ্ডা করার মতো ওষুধ, হালকা মাত্রার ঘুমের ওষুধ, এন্টি এংজাইটি বা দুশ্চিন্তারোধক ওষুধ সেবনের মাধ্যমে ডাক্তারগণ চিকিৎসা করতে পারেন। কারণ, এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে রোগীর পর্যাপ্ত মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন।
কাছের কেউ এই রোগে আক্রান্ত হলে আপনার যা করণীয়
আপনি এতদূর পড়ে হয়ত বুঝতে পারলেন আপনার কাছের কেউ ইতোমধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার ভেঙ্গে পড়া চলবে না। আপনি যা যা করতে পারেন তা হলো-
1.তিনি যে কোনো একটা রোগে ভুগছেন এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসুন। ফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষেরা সাধারণত ‘রোগী’ নয়, এমনকি তারা মানসিক রোগীও নয়। এরা সাময়িকভাবে একটা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে যা তারা নিজেরাও জানে না। অতএব তাদের সাথে সেভাবেই কথা বলুন।
2.স্বাভাবিক থাকুন। তাকে কখনই বুঝতে দেয়া যাবে না আপনি তার সাথে কোনোরকম পরামর্শে যাচ্ছেন যেটা তার কোনো সমস্যার সমাধান দিবে।
সঙ্গ দিন। এই সময়ে আক্রান্ত ব্যক্তির ভরসা করার মতো একজন মানুষের প্রয়োজন।
3.তার আস্থার ব্যক্তি হন, কিন্তু নির্ভরশীলতার নয়। ব্যাপারটা একটু জটিল হতে পারে। কিন্তু এই রোগ থেকে পরিত্রাণের এটাই উপায়।
4.আক্রান্ত ব্যক্তিকে একা একা চলাফেরা করার সুযোগ করে দিন। সেটা হতে পারে কোনো পার্ক, শপিং মল কিংবা রেস্টুরেন্ট। আপনি সাময়িকভাবে একটু দূরে সরে যেতে পারেন অথবা তাকে একাই কেনাকাটা করতে বলতে পারেন। এই সময় আপনি একটু দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কোনো সমস্যা হলেই যেন আপনি সামনে থাকতে পারেন এমন দূরত্ব বজায় রাখুন।
5.তাকে আত্মনির্ভরশীল হলে সাহায্য করুন। ‘তুমি একাই পারবে’ এই ধরনের মনোভাব গড়ে উঠতে সাহায্য করুন। বিভিন্ন কাজ তাকে একাই করতে দিন। মাঝেমাঝে হালকা ধাঁচের ধাঁধা সমাধান করতে দিন। পড়তে দিতে পারেন কিছু গোয়েন্দা ভিত্তিক বই। পরবর্তীতে হয়ত শুনে নিলেন সে কেমন বোধ করছে অথবা কাউকে তার দোষী মনে হচ্ছে কিনা।
6.এই ধরনের মানুষেরা নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে না, ফলে যেকোনো বিপদজনক পরিস্থিতিতে কেউ পাশে না থাকলে তার আতংকের সৃষ্টি হয় এবং সে ধরেই নেয় কাজটি তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই তাকে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল করে তুলুন।
আমাদের অজান্তেই হয়ত আশেপাশের অনেকেই এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণতাও এই ধরনের ফোবিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে প্রতিটি মানুষেরই নিজের উপরে নির্ভরশীল হতে শেখা উচিত। ব্যস্ত জীবনে হয়ত সবচেয়ে কাছের বন্ধু অথবা পরিবারের মানুষগুলোই একে অপরকে ঠিকমত সময় দিতে পারে না। এমন অবস্থায় যেন যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা একাই করা যায় এমন মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। আপনি, আমি আমাদের আশেপাশের সবাই যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো ফোবিয়ায় নিজেদের অজান্তেই আক্রান্ত হয়ে যেতে পারি। তাই নিজেকে মানসিকভাবে শক্ত রাখুন। এটাই মনোফোবিয়া থেকে নিরাপদ থাকার প্রধান উপায়। আত্মনির্ভরশীল হোন, সুস্থ থাকুন।
হিমোফোবিয়া: রক্ত যখন ভয়ের কারণ
নিজের স্ত্রীকে জন্মবার্ষিকীর সারপ্রাইজ দিয়ে গিয়ে নিজেই যে চমকে যাবে, সেটা ভুলেও ভাবেনি সৈকত (ছদ্মনাম)। কে চিন্তা করতে পেরেছিলো, বেলুনের মধ্যে ঢোকানো লাল রংয়ের তরল দেখে শ্বেতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার মতো কান্ড ঘটাবে?
মাত্র কিছু দিন হলো বিয়ে হয়েছে তাদের দুজনের। বিয়ের পরে শ্বেতার এটাই প্রথম জন্মবার্ষিকী। তাই সৈকত ভেবেছিলো শ্বেতাকে না জানিয়েই একটা জমকালো আয়োজন করে চমকে দেবে। সেই মোতাবেক ব্যবস্থাও নিয়েছিলো সে। পুরো ঘর সাজিয়েছিলো বিচিত্র সব বেলুন, কাগজ আর ফিতায়। বেলুনগুলো ভর্তি করা হয়েছিলো নানা রঙের তরল দিয়ে। দিনশেষে ওগুলোই হয়ে দাঁড়ালো বিপত্তির কারণ।
জন্মদিনের কেক কাটা শেষ হওয়া মাত্রই দেয়ালে টাঙানো বেলুনগুলো ফাটাতে শুরু করে ক্ষুদে অতিথিরা। সেগুলোরই একটার ভেতরে ছিলো লাল রং গোলানো পানি। বেলুনটা ফাটতেই ভেতরের তরলগুলো ছিটিয়ে পড়ে চারদিকে। এ দৃশ্য থেকেই চিৎকার করে জ্ঞান হারায় অনুষ্ঠানের মধ্যমণি শ্বেতা।
সাথে সাথে এগিয়ে আসেন অনুষ্ঠানের অতিথি শ্বেতার মামা। জ্ঞান ফেরাতে মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে তিনি সৈকতকে জানান, লাল রঙকে রক্ত ভেবে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে মেয়েটি। সেদিনই সৈকত জানতে পারে, শ্বেতার রয়েছে এক বিচিত্র অসুখ, যার নাম হিমোফোবিয়া বা রক্তভীতি।
হিমোফোবিয়া কী?
হিমোফোবিয়া শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দাংশ 'haima' এবং 'phobos' থেকে, যাদের অর্থ যথাক্রমে রক্ত এবং ভয়। অর্থাৎ হিমোফোবিয়ার সহজ সরল অর্থ হলো রক্তকে ভয় পাওয়া। সেই রক্ত হতে পারে নিজের, কিংবা অন্য কোনো মানুষ অথবা পশুপাখির।
যারা এ ফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা যে শুধু রক্তকেই ভয় পান তা নয়, রক্ত সম্পর্কিত যেকোনোকিছু দেখলেই তারা আঁতকে ওঠেন। এটি হতে পারে দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন, ঘাঁ, কাটাছেঁড়া; কিংবা বিভিন্ন বস্তু যেগুলোর সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন- সিরিঞ্জ, ইনজেকশন, এবং ছুরিকাঁচি।
এই অমূলক ভীতির কারণে এসব মানুষের জীবনযাপন দূর্বিষহ হয়ে ওঠে। হাত কেটে যাবে এই ভয়ে গৃহিণীরা ঘরের কাটাকুটিতে ছুরি-বটিতে হাত লাগাতে চান না। ছোট বাচ্চাকাচ্চা, এমনকি অনেক প্রাপ্তবয়স্কের কাছে ইনজেকশন হয়ে দাঁড়ায় এক ভীতির বিষয়, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তাদের চিকিৎসায়। এই ফোবিয়া প্রভাব ফেলে পেশা নির্বাচনেও। অনেকে তো শুধু রক্ত দেখতে হবে বলে চিকিৎসক হওয়ার আশা ছেড়ে দেন।
হিমোফোবিয়া ও ইতিহাস
ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, রক্তের প্রতি মানুষের ভীতি চিরায়ত। বিভিন্ন সাহিত্যিক কর্মের মধ্যে রক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভয়াবহতা, অপরাধ আর ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে।
তাই তো গ্রিক কবি হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যে আমরা দেখতে পাই মহাবীর অ্যাকিলিস বিপক্ষ ট্রোজান সৈন্যদের কচুকাটা করতে করতে এমন অবস্থা করেন যে জলধারা পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। আর রক্ত যে অপরাধের চিহ্ন, তা শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের লেডি ম্যাকবেথের রক্তাক্ত হাত পরিষ্কার করার প্রাণান্তকর চেষ্টা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।
এ কারণে রক্তকে ভয় পাওয়ার বিষয়টি আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সমস্যাটা তখনই দেখা দেয়, যখন ক্ষেত্রবিশেষে এই ভয়টা মাত্রাতিরিক্ত ও অমূলক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কেউ কেউ টমেটো সস দেখেই রক্ত ভেবে আতঁকে ওঠেন।
কারণ ও রিস্ক ফ্যাক্টর
গবেষকদের মতে, তিন থেকে চার শতাংশ মানুষের রক্ত দেখলে ভয় পেয়ে ওঠার বাতিক রয়েছে। সাধারণত ছেলেরা গড়ে ৯ বছর এবং মেয়েরা সাড়ে ৭ বছর বয়স থেকে রক্তভীতিতে ভুগতে শুরু করে। বেশ কিছু নিয়ামক রয়েছে, যেগুলো হিমোফোবিয়ার জন্য দায়ী। এগুলো হলো:
বংশগতির প্রভাব: অনেকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্তভীতি পেয়ে আসেন।
অনুকরণ: আমরা জানি, সকল ফোবিয়াই কারো না কারো কাছ থেকে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই নিজের আশেপাশের মানুষদের রক্তের প্রতি ভয় পেতে দেখলে, নিজের মধ্যেও হিমোফোবিয়া গড়ে ওঠে।
ট্রমাটিক ঘটনা: রক্ত নিয়ে পূর্বে কোনো ট্রমাটিক ঘটনা ঘটে গেলে তা মানুষকে হিমোফোবিয়ার দিকে ধাবিত করে।
উপসর্গ
একজন হিমোফোবিয়াক রক্তের সংস্পর্শে আসলে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকেন।
শারীরিক উপসর্গ
1.শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া।
2.হৃদকম্পন বেড়ে যাওয়া।
3.মাথা ঘোরানো ও বুকে ব্যথা হওয়া।
4.ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা।
5.বমি বমি ভাবের উদ্রেক ঘটা।
6.শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেয়ে পড়তে থাকা।
মানসিক উপসর্গ
1.প্রচন্ড ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়া।
2.চারপাশ থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়া।
3.দেহের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে, এমন অনুভূত হওয়া।
4.এখনই মারা যাবো এমন অনুভূত হওয়া।
যেভাবে দেখা দেয় উপসর্গগুলো
হিমোফোবিকরা রক্ত দেখলে কী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে সেটি নিয়ে হয়েছে বিস্তর গবেষণা। গবেষকদের মতে, রক্তের প্রতি হিমোফবিকরা মূলত দুই পর্যায়ে সাড়া প্রদান করে থাকে।
একজন হিমোফোবিক যখনই রক্তের সংস্পর্শে আসেন, তখনই রক্তভীতির কারণে তার মধ্যে উচ্চ শারীরিক ও স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে হৃদকম্পন, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার ও রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, চোখের মণি বড় হয়ে যাওয়া ও ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা। মূলত বিভিন্ন উদ্দীপক হরমোনের নিঃসরণ এর জন্য দায়ী।
দ্বিতীয় ধাপে ঘটে উল্টো ঘটনা। যে হরমোনগুলোর কারণে শরীর উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়েছিলো, সেগুলোর নিঃসরণ কমে যেতে শুরু করে। ফলে শরীর ভারী হয়ে আসে, হাতের পেশিগুলোতে বল পাওয়া যায় না, দেহের শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় প্রক্রিয়ার গতি কমে যেতে থাকে। রক্ত সরবরাহ কমে যাবার জন্য ব্যক্তি জ্ঞানও হারিয়ে ফেলতে পারেন। দেখা গেছে, হিমোফোবিকদের মধ্যে ৮০ শতাংশই রক্ত দেখলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।
নিরাময় ও প্রতিরোধ
সত্যি বলতে, হিমোফোবিয়া প্রতিরোধে প্রথাগত ওষুধের চাইতে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর মনোবলই বেশি কাজে দেয়। মনে রাখতে হবে, রক্ত কেবল মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। একে ভয় পাবার কিছুই নেই।
হিমোফোবিয়া নিরাময়ে এক্সপোজার থেরাপি বেশ ফলাফল দিয়ে থাকে। এই থেরাপিতে রোগীকে বারবার রক্তের সংস্পর্শে এনে সেটির সাথে অভ্যস্ত করানো হয়। এতে করে রোগী বুঝতে পারে, রক্ত নিয়ে যে ভয় সে এতদিন পেয়ে আসছিলো, তা নিতান্তই অমূলক। এভাবে তার ভয় ও আতঙ্ক কেটে যায়।
কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এবং রিলাক্সেশন থেরাপি ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও রক্তভীতি কমিয়ে আনতে অ্যাপ্লাইড টেনশন নামের একটি কসরত কৌশল রয়েছে যেখানে ধাপে ধাপে শরীরের কিছু পেশির সংকোচন ও প্রসারণ করার মাধ্যমে উদ্বেগ কমিয়ে আনা সম্ভব। অ্যাপ্লাইড টেনশন কৌশলটি নিম্নরূপ:
১. বসে পড়ুন। মাথা বনবন করার পরিণতি হতে পারে জ্ঞান হারানো। তাই মাথা বনবন করতে শুরু করলে তাড়াতাড়ি বসে যাওয়া উচিত। না হলে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন।
২. নিজের হাত দুটোকে পায়ের কাছে নিয়ে আসুন। নিজের মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলুন, যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে আছেন। এভাবে কমপক্ষে ১০-১৫ সেকেন্ড থাকুন।
৩. দম ফেলুন ধীরে ধীরে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক চাপকে সামলে নিন। হাতের পেশিগুলোকে শিথিল করে ফেলুন।
৪. এরপর পায়ের পাতা দিয়ে ভূমির ওপর চাপ প্রয়োগ করুন। একইসাথে নিজের হাটুকে হাত দিয়ে চেপে ধরুন। একই কথা কনুইজোড়ার জন্যও প্রযোজ্য।
৫. এবার পায়ের পেশিকে শিথিল করে ফেলুন। যেভাবে আছেন, সেভাবেই ১৫-২০ সেকেন্ড যেতে দিন।
৬. নিজের শরীরকে নাড়িয়ে এমন একটি ভঙ্গিমা করুন, যেন আপনি উঠে দাঁড়াতে চলেছেন। এটা অনেকটা দরজায় কলিংবেল বাজলে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর মতো।
৭. পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমিয়ে আনুন।
৮. এভাবে শরীরের সবগুলো পেশির কসরত সমাপ্ত হলে বুঝে নিন, আপনার সমস্ত শরীর এখন আশঙ্কামুক্ত।

অ্যাক্রোফোবিয়া বা উচ্চতাভীতির আদ্যোপান্ত
উচ্চতাভীতিকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাক্রোফোবিয়া। গ্রিক শব্দ ‘acron’ অর্থ উচ্চতা এবং ‘phobos’ অর্থ ভয়। এই শব্দ দু’টো নিয়েই ‘Acrophobia’ নামের উৎপত্তি।
উচ্চতাভীতি কী?
প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন জানান যে, তারা উঁচু কোনো জায়গায় গেলে এক ধরনের অস্বস্তি বা চাপ অনুভব করেন। উঁচু জায়গায় গেলে এমন অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক এবং তারা কিন্তু অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত নন।
অ্যাক্রোফোবিয়া শব্দটি সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যেখানে ব্যক্তির মনে উচ্চতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে দীর্ঘ সময় ধরে অযৌক্তিক, তীব্র ভয় কাজ করবে। অতিরিক্ত ভয় ও উদ্বেগের কারণে উঁচু কোনো জায়গা থেকে নেমে আসাটাও তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।
অ্যাক্রোফোবিয়াক ব্যক্তিরা উঁচু জায়গা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। উঁচু স্থানে গেলে বা যাওয়ার আশঙ্কা করলে তাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে, যার কাজ শরীরকে জরুরী অবস্থার জন্যে প্রস্তুত করে তোলা। এর ফলে শরীর আসন্ন বিপদের মোকাবেলা করা অথবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়, সাধারণভাবে যা ‘ফাইট-অর-ফ্লাইট রেসপন্স’ নামে পরিচিত।
এ সময়ে ব্যক্তিটি মাথা ঘোরানো, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, ঘাম হওয়া, কাঁপুনি এবং বমি বমি ভাব অনুভব করতে পারেন। সাধারণভাবে বিপজ্জনক কোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ‘ফাইট-অর-ফ্লাইট রেসপন্স’ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ‘বিপজ্জনক নয়’, এমন পরিস্থিতিতেও ‘ফাইট-অর-ফ্লাইট রেসপন্স’ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি অনেক সময় ব্যক্তিটি শ্বাসকষ্ট, নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারা বা মৃত্যুভয়েও আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন।
মানব মনে কীভাবে অ্যাক্রোফোবিয়া তৈরি হয়?
কেন মানুষের মধ্যে অ্যাক্রোফোবিয়া বা উচ্চতাভীতি গড়ে ওঠে, তার কারণ দু’ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, বিবর্তনমূলক এবং আচরণমূলক।
বিবর্তনমূলক মনোবিজ্ঞান অনুসারে, ভয় হচ্ছে মানুষের জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উচ্চতার সংস্পর্শে না আসলেও একজন মানুষ উচ্চতা সম্পর্কে ভয় পোষণ করতে পারেন।
বিবর্তনমূলক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অ্যাক্রোফোবিয়াক ব্যক্তিরা যে কোনো উপায়ে বিপজ্জনক উঁচু এলাকা এড়িয়ে চলেন। ফলে তারা বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকেন, টিকে থাকেন এবং পরবর্তীতে বংশ বিস্তার করেন। আর এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের জিন বাহিত হয়ে চলে।
মানব মনে সহজাত বা Innate Phobia মূলত এমন কোনো বস্তু বা পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়, যার সাথে মানুষকে দীর্ঘকাল মোকাবেলা করে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়েছে। যেমন- অধিক উচ্চতা বা সাপের প্রতি ভীতি। কিন্তু কেউ কেউ ডাক্তারের কাছে যেতে বা বক্তৃতা দিতে যে ভয় পান, তার উৎপত্তির ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।
এদিকে বিহেভিয়ারিস্টরা মনে করেন, ভয় সহজাত বা জন্মগত প্রবৃত্তি নয়, বরং আমরা ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিংয়ের মাধ্যমে ভয় পেতে ‘শিখি’। একটি উদাহরণ থেকে ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিং কীভাবে কাজ করে, সেটির পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি প্রথমবারের মত গাছে চড়েছেন। গাছে চড়ার পর স্বাভাবিকভাবে ঐ উচ্চতায় তিনি হয়তো ভয় অনুভব করবেন না। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে তিনি যদি গাছ থেকে পড়ে যান, তাহলে গাছে চড়ার ব্যাপারে তার মনে এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। উঁচুতে ওঠার পর পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার এই অভিজ্ঞতা তাকে উচ্চতার প্রতি নেতিবাচক ভাবাপন্ন করে তুলবে। ফলে পরবর্তীতে তিনি উঁচু জায়গা এড়িয়ে চলতে চাইবেন।
যদিও অনেক সময় দেখা যায়, একজন ব্যক্তি বাস্তবে কখনো একটি বিশেষ বস্তু বা অবস্থার সম্মুখীন না হওয়া সত্ত্বেও সেই বিশেষ বস্তু বা অবস্থার প্রতি ভয় অনুভব করেন। ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিং তত্ত্ব থেকে এ ধরনের ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।
সুতরাং অ্যাক্রোফোবিয়া কীভাবে মানুষের মনে স্থান করে নেয়, তা বুঝতে হলে বিবর্তনমূলক এবং আচরণমূলক- উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এর উৎপত্তি বিবেচনা করতে হবে।
চিকিৎসার মাধ্যমে কি এটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব?
অ্যাক্রোফোবিয়া কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রথমেই যা দরকার, তা হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তির আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা। তিনি নিজে যদি ভয় থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে মনোবিজ্ঞানী বা মনোচিকিৎসক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে তাকে ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন।
1.ইতিবাচক চিন্তা করা, মেডিটেশন, হিপনোসিস এক্ষেত্রে কাজে দিতে পারে।
2.ভয় কাটিয়ে ওঠার চিকিৎসা হিসেবে ‘সিস্টেম্যাটিক ডিসেনসিটাইজেশন’ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে রোগীকে নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ পরিবেশে রেখে ধীরে ধীরে তার ভয়ের সম্মুখীন করা হয়। যেমন- অ্যাক্রোফোবিক ব্যক্তিকে মই বা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা এবং ধীরে ধীরে ধাপ সংখ্যা বাড়িয়ে অধিকতর উচ্চতায় উঠতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, উঁচু দালান বা পাহাড় থেকে তোলা ছবি দেখানো হয়। এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এরপর রোগীকে উঁচু দালানের ব্যালকনি বা ছাদ থেকে নিচে তাকানো, চলন্ত সিঁড়িতে চড়া- এসব কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তার ভয় কাটানো যেতে পারে। তবে এ সময় বিশ্বস্ত কেউ অবশ্যই রোগীর সঙ্গে থাকা জরুরী।
3.রোগীর উদ্বেগ কাটানোর জন্যে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে কিছু ঔষধও সেবন করতে হতে পারে।
4.এটির চিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে- ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি এক্সপোজার থেরাপি (VRET)। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসা এ পদ্ধতিটি অ্যাক্রোফোবিয়ার চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর বলে জানা যায়।
‘ফিয়ার অব হাইট’ নামক একটি গেইমের বর্ণনা দিলে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি’র মাধ্যমে কীভাবে উচ্চতা-ভীতি কাটানো হয়, তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ২০১৬ সালে এপ্রিলের ১৫ তারিখে জাপানি ভিডিও গেইম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Bandai Namco Entertainment Inc. টোকিওর এক ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি এক্সপো সেন্টারে তাদের বিভিন্ন গেইম প্রদর্শন করেছিলো, যার মধ্যে ‘ফিয়ার অব হাইট’ অন্যতম। এই গেইমটিতে VRET থেরাপির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে একটি কাঠের পাটাতনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে একটি ছোট পুতুল বিড়ালের ছানাকে উদ্ধার করতে হয়।
আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি সাধারণ মনে হলেও গেমে অংশগ্রহণকারীর জন্যে এটি বেশ জটিল, কারণ গেমে অংশ নেওয়ার সময় তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় একটি হেডসেট, যা তাকে নিয়ে যাবে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি’র জগতে। তার মনে হবে তিনি উঁচু একটি দালানের চলন্ত এলিভেটরের ভেতরে আছেন। ষাট তলায় পৌঁছে এলিভেটর থামার পর দরজা খুলে গেলে তিনি দেখতে পাবেন, তার সামনে রয়েছে একটি কাঠের পাটাতন যার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিড়াল ছানা। যেকোনো সময় বিড়াল ছানাটি পাটাতন থেকে পড়ে যেতে পারে। যদিও বাস্তবে পাটাতনটি ঘরের মেঝেতেই রাখা হয়েছে, কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়্যালিটিতে এটিকে মাটি থেকে প্রায় ২০০ মিটার উচ্চতায় দেখানো হবে। অংশগ্রহণকারীর কাজ হচ্ছে বিড়াল ছানাটিকে পাটাতনের অপর প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা। এভাবেই ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির সাহায্যে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই একজন অ্যাক্রোফোবিয়াক তার ভয়ের সম্মুখীন হন এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি তার ফোবিয়া কাটিয়ে উঠতে বেশ সহায়ক হয়।
শুধুমাত্র উচ্চতা সম্পর্কে ভীতি ও উদ্বেগের কারণে রোলার কোস্টার রাইডে চড়া, পাহাড়ে ওঠা, বিমানে ভ্রমণ করা, বাঞ্জি জাম্পিং, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো অনেক উত্তেজনাকর আর উপভোগ্য মুহূর্তগুলো জীবন থেকে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমনকি সমস্যা হতে পারে দৈনন্দিন জীবনে সিঁড়ি বা মই বেয়ে ওঠা, এলিভেটর ব্যবহার করা, উঁচু দালানের ছাদ বা ব্যালকনিতে দাঁড়ানো, ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করার মতো সাধারণ কাজেও।
সুতরাং পাঠক, আপনার বা আপনার পরিচিত কারো মধ্যে উচ্চতা সম্পর্কে অতিরিক্ত ভীতি বা উদ্বেগ দেখা দিলে অবহেলা না করে একজন মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন, কাটিয়ে উঠুন অকারণ ভীতি।

আপনার কি টেলিফোবিয়া আছে?
ফোন বেজে উঠলেই কি আপনার ঘাম ছুটে যায়? বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা কোনও স্বাভাবিক বিষয় নয়! এটা এক ধরনের রোগ, যার নাম টেলিফোবিয়া৷
কী এই ফোবিয়া?
শুধু এই দেশে নয়, বিদেশেও এই রোগে আক্রান্ত বহু মানুষ৷ বয়স বা লিঙ্গভেদে এই রোগে আক্রান্ত মানুষ রয়েছেন প্রায় সব ক’টি মহাদেশেই৷ কী করে বুঝবেন আপনি এই রোগে আক্রান্ত? আচ্ছা, আপনি কি এসএমএস করতে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন? যাঁরা টেক্সট মেসেজ করতে পারদর্শী, কিন্তু ফোনে কথা বলতে গেলেই আমতা আমতা করেন, তাঁরাই নাকি এই রোগের শিকার৷
এই রোগ যে শুধু স্মার্টফোন ইউজারদেরই হয় এমনটা নয় কিন্তু! ১৯২৯-তে ব্রিটিশ কবি ও লেখক রবার্ট গ্রেভসও এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছে, শুধুমাত্র ফোনে কথা বলতে গেলেই এই রোগীরা ভয় পান এমনটা নয়৷ কথোপকথন মাত্রই তাঁরা পিছিয়ে আসেন৷ অনেকেই টেলিফোনে এই ভেবে কথা বলতে ভয় পান, যে তাঁরা যেন ভুলভাল কিছু বলে না বসেন! তবে নিয়মিত চেষ্টা করলে এই ভীতি কাটিয়ে ওঠা যায় বলেও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
ম্যাথেমাফোবিয়া: গণিতের ভীতি এবং সমস্যার সমাধান
ফরাসি স্কুলছাত্র লরেন সোয়াজ, অংক করতে বসলেই তার হাত-পা ঘেমে একাকার। নিজের উপর খুব সহজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে, সে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। শুধু এই লরেন সোয়াজই নয়, দুনিয়া জোড়া শত সহস্র মানুষের একই সমস্যা। অংকের সমাধান করতে বসলেই হাত-পা ঘামা শুরু হয়, মস্তিষ্ক কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে, চরম পরাজয়ের মতো অস্বস্তি বোধ হয়। তবে আপনারও যদি একইরকম হয়ে থাকে, তবে আপনি মোটেও একা নন, গবেষকদের মতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় বিশ শতাংশ এই ধরনের গণিত নিয়ে ভীতিতে ভুগে থাকে। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদের মতে, এই গণিত ভীতি একধরনের চিকিৎসাযোগ্য মানসিক সমস্যা। তবে এই সমস্যায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি যে গণিতে ভালো করতে পারে না, তা মোটেই সত্য নয়। গণিতকে ভয় পাওয়া সেই ফরাসি স্কুলছাত্র লরেন সোয়াজ পরবর্তীতে গণিতের সর্বোচ্চ সম্মান ফিল্ডস মেডেলে ভূষিত হয়েছিলেন।
গণিতভীতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন মেরি ফিডেস গফ নামের এক গবেষক। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রথম তার লেখায় ‘Mathemaphobia’ নামে শব্দটির প্রচলন করেন। গণিতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভীতি আর তার প্রতিকারে কী করা যেতে পারে, তা ছিলো এই গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু। পরবর্তীতে স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শত-সহস্র ছাত্র ছাত্রীর উপরে গণিতের ভয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে।
বর্তমান সময়ের মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, বেশিরভাগ মানুষের এই গণিত কিংবা সংখ্যার প্রতি বিদ্যমান ভীতি লুকিয়ে আছে তাদের মস্তিষ্কে। যারা গণিতকে ভয় পায়, তাদের অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল যে তারা গণিতে খারাপ। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনা কিছুটা উল্টো। তারা গণিত নিয়ে ভয়ে থাকে বলেই তাদের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা কম। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, মানুষ যখন গণিত সমাধানের ব্যাপারটি নিয়ে শংকিত হয়ে যায়, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিক জ্বালানিতে টান পরে। আর সেই জ্বালানি হলো ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুতগতির স্মৃতিশক্তি ব্যবস্থা, যা ‘ওয়ার্কিং মেমরি’ নামেও পরিচিত। এই স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী হলেও কোনো কাজের তথ্যগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে এর বিকল্প নেই। কঠিন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ কিংবা সমস্যা সমাধানে এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তির ভূমিকা আরো বেশি। গণিত সমাধানের ক্ষেত্রে এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির সিংহভাগই ব্যবহার করতে হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, গাণিতিক সমস্যা নিয়ে শুরুতেই যদি কেউ ভীত হয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির অনেকটাই নেতিবাচকতা এবং এর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কাজেই ব্যস্ত হয়ে যায়। গাণিতিক সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য খুব অল্পই অবশিষ্ট থাকে। ফলে দেখা যায় গণিতভীতিতে ভুক্তভোগীদের অনেকেই মানসিক চাপে সাধারণ যোগ-বিয়োগেও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। প্রতিযোগিতা কিংবা পরীক্ষায় এই ধরনের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে অনেকের মাঝেই।
তবে শিশু কিংবা তরুণদের মধ্যে গণিত নিয়ে ভীতির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিংবা প্রাপ্তবয়স্কের অনেকেও এই সমস্যায় জর্জরিত। দোকানে কিংবা বাজারের ফর্দ দেখেও অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে যান। তবে ব্যাপারটি শুধুই আমাদের মনেই ভীতির সঞ্চার করে না, অনেক মানুষ গণিত সমাধান করতে রীতিমতো যন্ত্রণা অনুভব করেন।
গবেষকদের দীর্ঘদিন ধরে চালানো গবেষণায় দেখা গেছে, গণিতের প্রতি ভীতি থাকা ব্যক্তিদের গাণিতিক সমস্যা দিয়ে কোনো পরীক্ষা কিংবা প্রতিযোগিতায় বসিয়ে দিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ‘কর্টিসল’ নামক হরমোন নিঃসরিত হয়। এই হরমোন আমাদেরকে অধিকমাত্রায় উত্তেজিত করে দেয়। পাশাপাশি এই ধরনের প্রতিযোগিতা কিংবা পরীক্ষা আমাদের মস্তিষ্কের এমন কিছু স্থানকে (পেইন ম্যাট্রিক্স) উত্তেজিত করে, যেগুলো আমরা সাধারণত ব্যথা পেলেই কার্যকর হয়।
তবে এমনটা হওয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকা কারণটা বের করতেও কাঠখড় কম পুড়িয়ে যাচ্ছেন না গবেষকরা। তবে তাদের ধারণা, শিশুদেরকে খুব কম বয়সে যেভাবে গণিতের হাতেখড়ি দেওয়া হয়ে থাকে, সে ব্যাপারটিও কোনো অংশে কম দায়ী নয়। বেশিরভাগ শিশুর সামনেই তার পরিবার কিংবা শিক্ষক উভয়েই গণিতকে বিভীষিকা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এমনকি অনেক কম বয়স থেকেই বেঁধে দেওয়া সময়ে গণিতের সমাধান করতে দেওয়াও ভীতির সঞ্চার করে শিশুদের মধ্যে। বিশেষ করে মেয়েরা গণিত সমাধানে কম দক্ষ, এমন মানসিকতাও বিদ্যমান অনেকের মধ্যেই। তবে ব্যাপারটি মোটেই সত্য নয়। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন গবেষণা বলছে, গাণিতিক সমস্যা সমাধান দক্ষতা আমাদের লিঙ্গের সাথে যতটা না জড়িত, তার চেয়ে অনেক বেশি জড়িত আমাদের সংস্কৃতির সাথে। ছোটবেলা থেকেই মেয়ে শিশুদের মধ্যে গণিত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দিয়ে দিলে পরবর্তী জীবনে তা উৎরে যাওয়া খানিকটা কঠিন। এমনকি গণিতের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান ফিল্ডস মেডেল পাওয়া প্রথম নারী গণিতবিদ মরিয়ম মির্জাখানিও স্কুলে পড়ার সময়ে গণিতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, কারণ তার শিক্ষকেরা মনে করতো মরিয়মের গণিত সমাধান করার মতো প্রতিভা নেই।
তবে গবেষকদের ধারণা, গণিতের প্রতি বিদ্যমান এই ভীতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। মূলত যেকোনো প্রতিযোগিতায় গণিতকে কেন্দ্র করে ভীতি এবং উত্তেজনাকে কাটিয়ে উঠতে একটি কার্যকর উপায় হলো এই ভীতিকে অন্যদিকে ধাবিত করে দেওয়া। এটি করা যেতে পারে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিয়ে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উত্তেজিত মুহূর্তেও নিজেকে শিথিল করা যায়। কর্টিসল হরমোনের প্রভাবে সৃষ্ট উত্তেজনার ফলে অনেক সময় আমাদের হাত-পা কাঁপতে থাকে কিংবা অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার যে ব্যাপারটি দেখা যায়, সেটিও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
গণিতভীতিকে যেহেতু বর্তমান সময়ে একটি মানসিক সমস্যা হিসেবেও গণ্য করা হয়, সেটিকে দূর করার আরেকটি উপায় হলো গণিতের নিজের ভয়ভীতিকে লিখে ফেলা এবং সেগুলো মূল্যায়ন করা। ‘Expressive writing’ নামক প্রক্রিয়ায় নিজের সমস্যাগুলোর বিবরণ নিজেই খাতায় লিখে ফেলা হয় এবং এর ফলে ক্ষণস্থায়ী কার্যকরী স্মৃতির উপর চাপ অনেকটাই কমে আসে।
পরবর্তীতে মানসিকভাবে চাপমুক্ত অবস্থায় সেই বিষয়গুলোকে পুনরায় মূল্যায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কী করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। গণিত সমাধানে কাটিয়ে উঠতেও এই প্রক্রিয়া বেশ কাজে দেয়। এক জরিপে দেখা গেছে, এক দল কলেজ শিক্ষার্থীকে গণিত সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের ভয়ভীতির ব্যাপারে লিখে সেগুলো নিজেকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিলো। কয়েকমাস অন্তর অন্তর তাদের গণিতের ছোট ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের গড় নম্বর রেকর্ড করা হয়। এবং যাদের এই কাজ করতে বলা হয়নি, তাদের কয়েকজনেরও এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। উভয়ের গড় নম্বর তুলনা করে দেখা গেছে নিজের ভয়ভীতিকে লিখে সেগুলোকে মূল্যায়ন করা দলটি তূলনামূলক এগিয়ে আছে এবং গণিতের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবও অনেকাংশে দূরে সরে গেছে।
পাশাপাশি গণিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ভীতি কাটিয়ে উঠতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক যথেষ্ট মাত্রায় সহনক্ষম এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী। খুব ছোট বয়স থেকেই বাচ্চাদেরকে গণিত সমাধানে সময় বেঁধে দিয়ে তাদেরকে গণিতের প্রতি ভীত করে না তোলারও পরামর্শ দেন অনেক মনস্তত্ত্ববিদ। পাশাপাশি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে গণিতের প্রতি বিদ্যমান ভয় উল্লেখযোগ্য হারে দূর করা যায়। অনেকটা নতুন ভাষা শেখার মতো করেই প্রকৃতির এই ভাষা শেখার চেষ্টা করলে গণিত মোটেই কঠিন কিছু নয়।